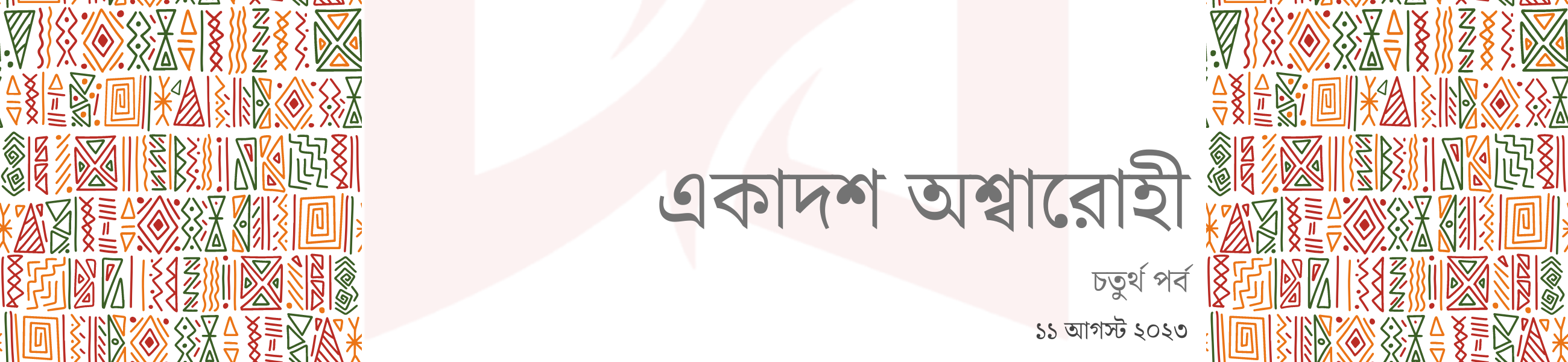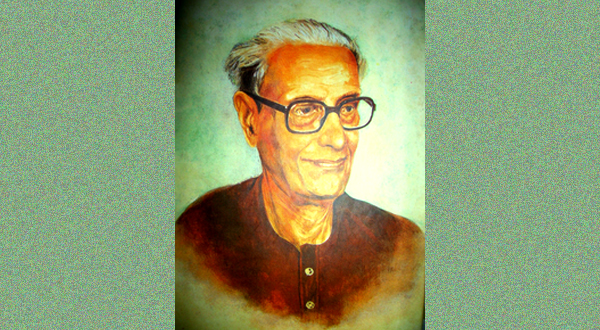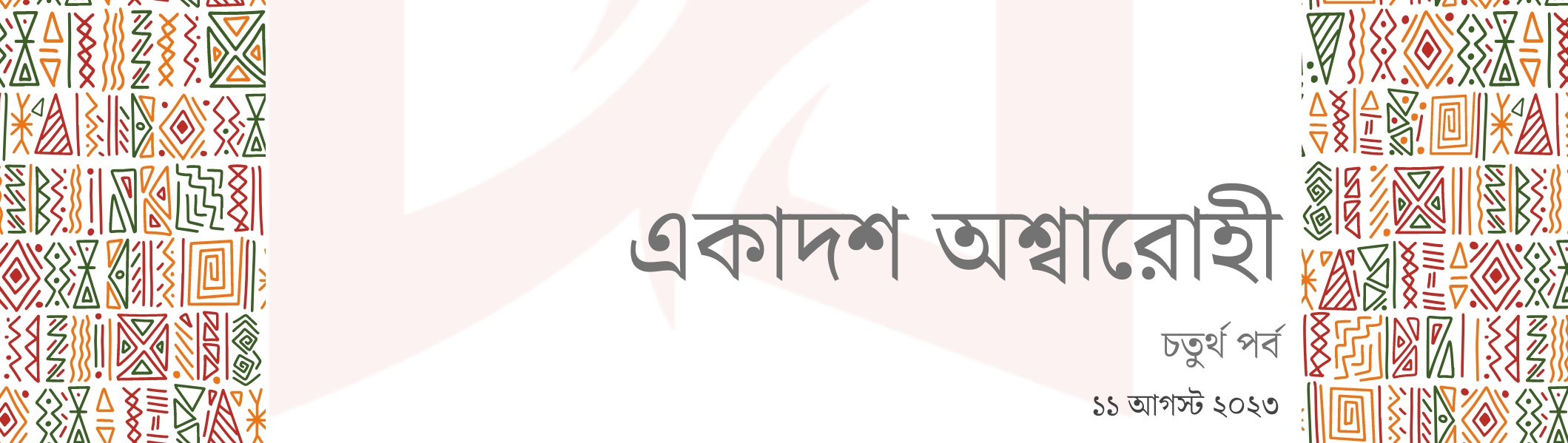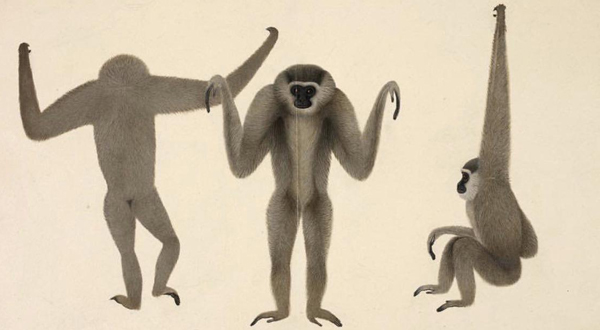তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি। কুমিল্লা জেলার জজের আসনে বসেছেন এক মধ্য তিরিশের বাঙালি যুবক। ওড়িশাতে জন্মগ্রহণ করলেও, মনে প্রাণে আদ্যোপান্ত বাঙালি। বাংলা সাহিত্য পড়েন, নিজেও নাকি টুকটাক লেখালেখি করেন। আইসিএস পরীক্ষাতেও রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছিলেন। কাজেই, দক্ষতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এদিকে একই সরকারি কাজকর্ম করতে করতে যুবকটির প্রাণ ওষ্ঠাগত। মুক্তির খোঁজে ছুটে যেতেন পুব বাংলার মাঠে ঘাটে। প্রকৃতি যেন মাতিয়ে তুলত তাঁকে। দিব্যি চলছিল সব। স্বাধীনতার লড়াইও চলছিল।
আরও পড়ুন
তখনও ছাত্রাবস্থা পেরোননি জসীম উদ্দীন, বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতা পড়ানো শুরু হল তাঁর
এমন সময় ঘটে গেল সেই ঘটনা। স্বাধীনতা এল তো বটে, কিন্তু ভেঙে দিয়ে গেল যাবতীয় বাঁধন। দেশভাগ যেন এক লহমায় বিদেশি করে দিল অনেককে। যুবক অন্নদাশঙ্কর রায় তখন চল্লিশে ঢুকে প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করেছেন। এমন ঘটনা কিছুতেই মানতে পারেননি তিনি। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কষ্ট পেয়ে গেছেন এর জন্য। সেই মুহূর্তে তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এল সেই অমোঘ কবিতাটি—
“তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর প’রে রাগ করো,
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো, তার বেলা?”
আরও পড়ুন
জাহাজ তাঁকে চিনিয়েছে পৃথিবী, কবিতা দিয়েছে ভাষা – এক বাঙালি নাবিকের গল্প
অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রসঙ্গ উঠলে অবধারিতভাবে উঠে আসবে এই কবিতাটির কথা। পরবর্তীকালে এই গানে সুরও আরোপ করেন সলিল চৌধুরী। আজও নানা সময় নানা আন্দোলনের মধ্যেও এই কবিতাটিই আশ্রয় করেন তরুণরা। ঠিক যেমন দেশভাগের সময় অন্নদাশঙ্করের আশ্রয় হয়েছিল এটি। বারবার আক্ষেপ করেছেন এই ঘটনা নিয়ে। একবার বলেওছিলেন, “…ছিন্ন হয়ে গেল পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আমার এতদিনের প্রশাসনিক সম্পর্ক। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বলতে যাকে বোঝায় তা পূর্ববঙ্গই। সোনার বাংলা যাকে বলা হয় সে-ও পূর্ববঙ্গ। হায়, সেখানে আমি বিদেশি।”
আরও পড়ুন
‘দেশ’ পত্রিকায় বাতিল কবিতা, নজরদারি আকাশবাণীতেও – জরুরি অবস্থার শিকার শঙ্খ ঘোষ
বাইরেই বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি। নানা সময় নানা কাজ করেছেন। সাংবাদিকতার সঙ্গেও যেমন যুক্ত ছিলেন, তেমনই সামলেছেন সরকারি গুরু দায়িত্ব। জীবনের সমস্ত কাজের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছিলেন সাহিত্যকেও। বাংলা, ওড়িয়া-সহ নানা ভাষার সাহিত্য অধ্যায়ন করেছিলেন তিনি। বিদেশ ভ্রমণকালে সেখানকার গল্পও লিখেছেন। সবভাবে যাতে বাংলার সঙ্গে থাকা যায়, সেই চেষ্টাই করে গেছেন সবসময়। শুধু লিখবেন বলেই ১৯৫১ সালে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেন সরকারি চাকরি, সম্মান। কীসের জন্য এই কৃচ্ছসাধন? কলমকে আঁকড়ে থাকবেন বলে। মাঝে মাঝে সত্যিই অবাক লাগে, অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো এত বড়ো মাপের সাহিত্যিক, শিল্পীরা আজকের এই ভোগসর্বস্ব, পুঁজিসর্বস্ব ইদুর দৌড়ের দুনিয়ায় জন্মালে কী করতেন?
আরও পড়ুন
বিদ্যাপতির ভাষা এখনও ঘোরে কলকাতায়, মৈথিলী কবি ভাস্কর ঝা’র বসবাস এই শহরেই
তখন নওগাঁর মহকুমা শাসক ছিলেন অন্নদাশঙ্কর। সেখানে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন অন্নদাও। দেখেছেন কবি’র মগ্নতা, সাধনা। যেন অন্য একটি রূপে ধরা দিলেন গুরুদেব। একবার আত্রাই ঘাটে অভ্যর্থনায় গেছেন অন্নদাশঙ্কর। স্টেশনে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বসে আছেন তিনি। অপেক্ষা কলকাতায় ফেরার। রবীন্দ্রনাথকে দেখে এগিয়ে এলেন অনেক মুসলিম বৃদ্ধ। কেউ সালাম জানাচ্ছেন, কেউ কুশল সংবাদ নিচ্ছেন। কেউ আবার কাঁদছেন। একসময় রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, “ওঁরা কী বলছে আমায়, জানো? বলেছে আমরা পয়গম্বরকে চোখে দেখিনি, আপনাকে দেখেছি।” পরে এই প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের বক্তব্য ছিল, “তখন রবীন্দ্রনাথের মুখে পীরের মতো দাড়ি, পরনে আলখাল্লা। তাঁকে দেখলে সত্যিই পীর বলে ভ্রম হওয়াটা স্বাভাবিক। এমনকি তাঁর জন্মও পিরালি বংশে।” খানিক ঠাট্টা করলেও, রবি ঠাকুর সম্পর্কে ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। কল্লোল যুগের অন্যতম প্রধান কবি, সাহিত্যিক হয়েও রবীন্দ্র-সাগরে ডুব দিয়েছেন তিনি।
আরও পড়ুন
ফয়েজের কবিতা কি হিন্দুত্ব-বিরোধী— বিচারে প্যানেল বসাল আইআইটি কানপুর
ওপার বাংলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি আরও একটি জিনিস জুড়ে আছে গভীরভাবে। লোকসঙ্গীত। অন্নদাশঙ্কর রায় রীতিমতো পাগল হয়ে গিয়েছিলেন এই ঘরানার সঙ্গীতে। সেই বাংলার টান, মাটির টান যেন খুঁজে পেতেন প্রতি পরতে। বাড়তে থাকে প্রকৃতি প্রেম। এই প্রকৃতিই তাঁকে টেনে নিয়ে যায় শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ, শিল্প আর পরিবেশ যে সেখানে একাকার হয়ে আছে! সেটা ১৯৫১ সাল। পরের বছরই ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দেয় পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন তরুণ। কয়েক মাইল দূরে বসে সেই আঘাত যেন নিজের মধ্যেও পেলেন অন্নদাশঙ্কর। ১৯৫৩ সালে শান্তিনিকেতনেই আয়োজন করেন এক সাহিত্য মেলার। পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, পূর্ব পাকিস্তান থেকেও এই মেলায় হাজির হন কাজী মোতাহার হোসেন, মহম্মদ মনসুরউদ্দিন, শামসুর রহমানরা। মূল লক্ষ্য, ভাষার সম্মান। ভাষার লড়াই।
আরও পড়ুন
কলকাতায় এলেন গালিব, তর্কে জড়ালেন অন্যান্য কবিদের সঙ্গেও
দুই বাংলা থেকেই পেয়েছেন অজস্র সম্মান। রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন দু’বার। সেই সময়ের তরুণ কবি লেখকদেরও কাছের হয়ে উঠেছিলেন। সাহিত্যের সব আঙিনাতেই তো ঘুরে বেরিয়েছেন তিনি। নিজেই হয়ে উঠেছেন একটি নাম। কল্লোল যুগের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠে এসেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। শুধু কলমই তাঁর কাছে একমাত্র আশ্রয় ছিল। যার জন্য সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ করেছিলেন তিনি। লেখাই যে তাঁর একমাত্র বেঁচে থাকার রসদ!
ঋণ-
সমকাল