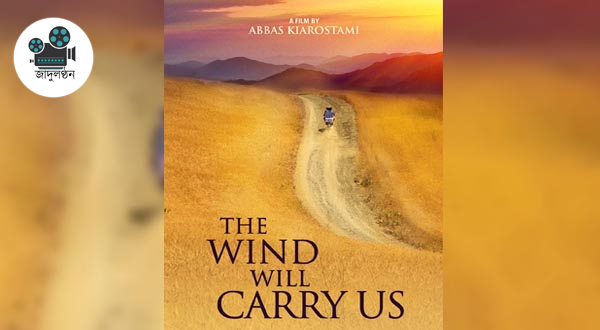তিনি, সুদীপ্তা সেনগুপ্ত। পেশায় জিওলজিস্ট। শখ ছিল মাউন্টেনিয়ারিং-এরও। সঙ্গ পেয়েছেন তেনজিং নোরগের। পৃথিবীর একাধিক পর্বতে অভিযান চালিয়েছেন। প্রথম বাঙালি মহিলা হিসেবে আন্টার্কটিকা অভিযানে গিয়েছিলেন তিনিই। সেসব অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, এই সাক্ষাৎকারে ধরা দিয়েছে জিওলজি সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও অভিজ্ঞতাও। কথোপকথনে সোহম দাস। আজ দ্বিতীয় পর্ব...
যাঁরা জিওলজি পড়েছেন, অনেককেই দেখেছি সুলেখক হয়েছেন পরবর্তীকালে। যেমন সঙ্কর্ষণ রায়। কবি উৎপলকুমার বসু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে জিওলজির ছাত্র ছিলেন। আপনি তো সামনেই বসে আছেন। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ছিলেন সেই স্বাধীনতার আগে, সুবীর ঘোষের কথা আপনি বললেন, এছাড়া, আমি আমাদের স্যারদেরও দেখেছি, তাঁদেরও সাহিত্য, সিনেমা, এসবে দারুণ জ্ঞান। এই বিষয়টা কি ওই জিওলজি পড়ার সূত্রে ফিল্ডে গিয়ে একটা ওপেন মাইন্ডেডনেস চলে আসে বলে হয়?
আমার যেটা মনে হয়, জিওলজির সঙ্গে যেহেতু প্রকৃতির একটা খুব নিবিড় সম্পর্ক আছে, সেটার জন্যে একটা ফিলোজফিক্যাল মাইন্ড ডেভেলপ করেই। একলা একলা যখন তুমি পাহাড়ে বসে আছ, এই তুমিই একটু আগে বলছিলে না, যে আমরা কত ক্ষুদ্র, ওই মনোভাবটারই একটা রিয়্যালাইজেশন হয়। সিংভূমে আমি যখন পিএইচডি-ও করতাম, অনেক সময়েই আমার একটা পাথর দেখে মনে হত, এর ওপর দিয়ে তো ডাইনোসররাও হেঁটে গেছে, আদিম মানবরাও হেঁটে গেছে। পাথরটার বয়সটা এত বেশি, যে পাথরটা তো দেখেছে পুরো এভোলিউশন। এরকম নানারকমের ফিলোজফিক্যাল রিয়্যালাইজেশন, এটা প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে থাকতেই চলে আসে।
আরও পড়ুন
‘আন্টার্কটিকা থেকে ফেরার পর, দেশ পত্রিকায় অভিজ্ঞতা লিখতে বললেন সাগরময় ঘোষ’
রবীন্দ্রনাথ যেমন ‘শেষ কথা’-য় নবীনমাধবের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন ‘পৃথিবীর ছেঁড়া স্তর থেকে বিপ্লবের ইতিহাস বার করাই আমাদের (ভূতত্ত্ববিদদের) কাজ’...
এত সুন্দর ভাষায় আর কে-ই বা বলতে পারেন, বলো। সে তো সত্যিই। এত বছরের ইতিহাসটা পাথরেই ধরা আছে পুরো। পুরো গল্পটা ওই কয়েকটা পাথর দেখেই তোমায় বলতে হবে।
ওঁর বাবা দেবেন্দ্রনাথও তো জিওলজি চর্চা করতেন…
হ্যাঁ, তখন ওই অবস্থাপন্ন ঘরের মানুষজন নেচার স্টাডি করতেন, তো সেইভাবেই জিওলজিটাও চর্চা তাঁরা করতেন।
আরও পড়ুন
ইনিংসের শেষ পর্যন্ত ব্যাটিং করতে চাই আমি, ‘শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই’-এর মতো
তবে সেই অর্থে বাংলা ভাষায় এই বিষয় নিয়ে সহজে বোঝানোর মতো বই তো খুব একটা হয়নি।
আসলে, এগনো যায়নি তো। এটা নিয়ে অনেকদূর চর্চা করে কেউ যদি লেখে, সেটা বেশ কঠিনই ব্যাপার। সুবীরবাবু একটা বই লিখেছিলেন হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলের। একটা সময়ে কথা উঠেছিল, জিওলজিটা হায়ার সেকেন্ডারিতে পড়ানো হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট থেকে সুবীরবাবুকে বলা হয়েছিল, স্ট্রাকচারাল জিওলজির বই লিখতে। উনি বাংলায় ‘গঠন-সম্পর্কীয় ভূবিদ্যা’ বলে একটি বই লিখেছিলেন। খুবই ভালো হয়েছিল বইটা। প্যালেন্টোলজি (পুরাজীববিদ্যা, জীবাশ্মের উপর পড়াশোনা) নিয়ে তবু বই লেখা হয়েছে, কারণ এটা পপুলার সাবজেক্ট তো, কিন্তু জিওলজির অন্যান্য শাখা নিয়ে খুবই কম লেখা হয়েছে।
আমার এই মুহূর্তে একটা বইয়ের নাম মনে পড়ছে, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী থেকে বার করেছিল, ‘যত কাণ্ড ফসিল নিয়ে’। সেখানে আমি প্রথম লা ব্রিয়া টারপিটের কথা জানতে পারি, সাইবেরিয়ার সেই উলি ম্যামথের কথা জানতে পারি…
হ্যাঁ, এরকম বই আরও বেশি করে লেখা উচিত। কারণ, এই বিষয়গুলো গল্পের মতো করে ছাত্রছাত্রীদের পড়ালে সেগুলো মাথায় ভালোভাবে গেঁথে যায়। কিন্তু, পাথরের বিষয়গুলো নিয়ে লেখা বই অন্তত আমার মনে পড়ছে না।
আরও পড়ুন
‘রজত কাপুরকে অনেক জ্বালানোর পরেও তাঁর পেশাদারিত্ব মুগ্ধ করেছে’ – ‘শব্দ জব্দ’ টিমের সঙ্গে আড্ডা
আপনি কখনও এই বিষয়গুলো নিয়ে লিখবেন বলে ভাবেননি?
লিখতে তো খুবই ইচ্ছে করেছে। কিন্তু ওই ‘আন্টার্কটিকা’ লিখতে গিয়েই আমি বুঝেছি, এ প্রায় একখানা থিসিস লেখার মতো। তোমাকে সবকিছু ছেড়েছুড়ে লিখতে হবে। তখন একটা নতুন জিনিস দেখে এসেছি ওই একাগ্রতাটা খুব হয়েছিল। ভেবেছিলাম, রিটায়ার করার পর লিখব, কিন্তু লিখেই উঠতে পারছি না। এই এক পাতা লিখি তো, সাতদিন বাদ পড়ে যায়। তবে ইচ্ছে তো আছে এখনও লেখার।
খানিক অন্য প্রসঙ্গে যাই। এখনও জিওলজি সম্পর্কে মানুষের তেমন ধারণা নেই। বেশিরভাগ মানুষই জিওলজিতে রিসার্চ শুনে প্রশ্ন করে ‘মাটি খুঁড়লে কি সোনা পাওয়া যাবে’ বা ‘তেল পাওয়া যাবে’। এই জায়গায় আমার মনে একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে যে, বিড়লা তারামণ্ডল যেমন নন-অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল মানুষজনকে ইন্ট্রোডাক্টরি অ্যাস্ট্রোনমির একটা কোর্স অফার করে, সেরকমই জিওলজির ক্ষেত্রে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান যদি সাধারণ মানুষকে অবগত করে তোলার দায়িত্ব নেয়, এ বিষয়ে আপনার কী মত?
হ্যাঁ, এটা খুবই ভালো প্রস্তাব। কারণ, দ্যাখো, স্কুল-স্তর থেকেই, মানে ক্লাস নাইন থেকেই মোটামুটি একজন ছাত্র বা ছাত্রীর ক্ষেত্রে, সায়েন্স পড়বে কী আর্টস পড়বে সেটা ঠিক হয়ে যায়। তারপর টুয়েলভের পরে কোন লাইনে যাবে, এটা তো স্টুডেন্টদের একটা বেশ চিন্তায় ফেলে। আজকাল তো অনেক সুযোগও হয়েছে, নানা বিষয়ের দিক খুলে গেছে। বায়োলজিক্যাল সায়েন্স সম্পর্কে মানুষের অনেক বেশি জ্ঞান থাকে, কিন্তু জিওলজি সম্পর্কে জ্ঞানটা সীমিতই। সেটার যদি সুযোগ করে দেওয়া যায়, তাহলে তো খুবই ভালো। ‘হোয়াট ইজ জিওলজি’ এই বিষয়টা যদি স্কুল-স্টুডেন্টদের মধ্যেই ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সেটা তো খুবই ভালো হয়। আর আজকাল পাওয়ারপয়েন্টে সবকিছু দেখানো যায়, সেরকম ইন্ট্রোডাকশন টু জিওলজি-র মতো কোনো একটা প্রেজেন্টেশন শহরের বাইরের স্টুডেন্টদের দেখানোই যায়।
আরও পড়ুন
ঋত্বিকবাবু পরিচালনা করলে ‘অযান্ত্রিক’-এ অভিনয় করতে চাই
আরও একটা বিষয়, যে, পৃথিবীর বয়সের সাপেক্ষে মানুষ এসেছে সবচেয়ে শেষে, কিন্তু তাতেই সে পৃথিবীর যা ক্ষতি করেছে, তা একেবারে চিন্তার বাইরে। সেকথা মনে করিয়ে দিতেও তো বোধহয় জিওলজি পড়ার প্রয়োজন আছে। এক অর্থে, পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে জিওলজির গুরুত্ব কতটা বলে মনে হয় আপনার?
হ্যাঁ, আমরা তো সত্যিই কতখানি ক্ষুদ্র, কত নগণ্য। আমাদের কোনো অধিকারই নেই এই পৃথিবীটাকে ধ্বংস করার। হিমালয়ও তো কত পালটে যাচ্ছে। করচা নালার ওখানে এখন শুনি বাস যায়। পুরো ব্যাপারটা মেকানাইজড হয়ে যাচ্ছে। আমরা যে কতখানি ক্ষুদ্র, সেটা মানুষকে বোঝানো খুবই দরকার।
এখন যারা জিওলজিতে রিসার্চ করছেন, তাঁদের অনেকের মুখে এই কথাটা আমি প্রায়ই শুনতে পাই যে, কোর পার্টের থেকে রিসার্চটা এখন অনেক বেশি অ্যাপ্লায়েড পার্টে ফোকাসড। অনেক জায়গায় পড়াশোনাও সেভাবেই হচ্ছে, সেই অ্যাপ্লায়েড-ওরিয়েন্টেড। সেটা কতটা গ্রহণযোগ্য?
আমার মনে হয়, শুধু জিওলজির ক্ষেত্রেই নয়, সব বিষয়ের ক্ষেত্রেই, ইট’স নট আ গুড সাইন। বেসটা যদি নেগলেক্টেড হয়, কতদিন আর তুমি অ্যাপ্লায়েড দিয়ে চালাবে! কারণ, কোরের রিসার্চের রেজাল্ট থেকেই তো অ্যাপ্লায়েড জিনিসটা আসে। অন্তত, প্রথম দিকে অর্থাৎ আন্ডারগ্র্যাজুয়েটে কোর সাবজেক্ট পড়াতেই হবে, উইথ রিয়েলি সিরিয়াস এমফ্যাসিস। তারপর পোস্টগ্র্যাজুয়েটে তুমি অ্যাপ্লায়েডে যেতেই পারো, কিন্তু আন্ডারগ্র্যাজুয়েটে কোরের উপরেই ফোকাসটা রাখা উচিত।
আরও পড়ুন
এই ছবি করার পর ‘পার্সেল’ এলে ভয়ও পেতে পারি: ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত
আমরা যেভাবে জিওলজি-টা পড়েছি, সেটাকে যেন খানিক ব্যাকডেটেড বলেই মনে হয়েছে। অনেকের মুখেই একথা বলতে শুনেছি, যে, কলকাতা এখনও অনেক পিছিয়ে আছে, মূলত কলকাতার ব্যাকগ্রাউন্ড যাদের, তাদের মুখেই। এটা কি সত্যি?
আমার এটা একেবারেই সত্যি বলে মনে হয় না। আমিও আগে এসবই শুনতাম। আমি যখন পড়াচ্ছি, তখন যখন বিদেশে যেতাম, তখন ওদেশের অধ্যাপকদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে, আমাদের ক্ষেত্রে নানারকম সুযোগ-সুবিধা সত্যিই সীমিত, বিদেশের সঙ্গে তুলনাই হয় না। আমি একজনকে বলেছিলাম যে, তোমরা তো অনেকরকম সুযোগ-সুবিধা পাও, তোমরা অনেক বেশি এগিয়ে আছ হয়ত। আমরা যা পড়াই, আমরা যেভাবে পড়াই, সেদিক থেকে আমরা হয়তো পিছিয়েই আছি। তখন একজন খুব নামকরা প্রফেসর আমাকে বলেন যে, আই ডোন্ট নো দ্যাট। দ্য ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস উই গেট হিয়ার আর ভেরি গুড। ইউ মাস্ট বি ডুয়িং সামথিং ভেরি স্পেশাল টু প্রিপেয়ার দোজ স্টুডেন্টস। সুতরাং, আমার মনে হয় না, এটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার আছে। ওই বেসিকটা যদি ঠিক করে তৈরি করে নাও, বাকিটুকু শিখতে সময় লাগে না। আমি এটাও বিশ্বাস করি যে, ভিত তৈরির জন্য খুব উন্নত টেকনোলজিরও দরকার নেই, বরং গোড়াটা ভালো তৈরি হয়ে থাকলে উন্নত টেকনোলজি শিখতে বেশি সময় লাগে না। একটা ব্ল্যাকবোর্ড আর একটা চকই যথেষ্ট। আমরা যাঁদের কাছে পড়েছি, তাঁরা তো ব্ল্যাকবোর্ড আর চকেই পড়িয়েছেন। আমার স্যার সুবীর ঘোষের কথা তো শুনেই থাকবে, তিনি তো ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস সায়েন্টিস্ট ছিলেন।
আরও পড়ুন
“আমি চাই, আমার সিনেমা দর্শককে বিব্রত করুক, অস্বস্তিতে ফেলুক”— ইন্দ্রাশিস আচার্যর সঙ্গে একটি আড্ডা
ভারতীয় জিওলজিস্টদের মধ্যে প্রফেসর সুবীর ঘোষ তো কিংবদন্তি মানুষ ছিলেন। তাঁর লেখা বই তো আমরা পড়েওছি। আপনি তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। আরও অনেককেই আপনি কাছ থেকে দেখেছেন। এঁরা বাকিদের থেকে কোন জায়গায় আলাদা ছিলেন?
আমি যখন যাদবপুরে আন্ডারগ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হই, তখন সুবীরবাবুর ক্লাস প্রথম করি। খুব নিচুস্বরে পড়াতেন, আর এত আন-অ্যাজিউমিং ছিলেন, যে, খুব সহজ ভাষায় কঠিন জিনিস পড়িয়ে দিতে পারতেন। স্ট্রাকচারাল জিওলজির প্রতি আমার ভালবাসা তৈরিই হয় সুবীরবাবুর জন্য। তখনই আমি ঠিক করি, আমি সুবীরবাবুর কাছেই স্ট্রাকচারাল জিওলজিতে রিসার্চ করব। পিএইচডি থিসিস আমি সুবীরবাবুর কাছেই করি। উনিই প্রথম ডিপার্টমেন্টে নিজের ঘরের পাশে মডেল ডিফরমেশন ল্যাব তৈরি করেন, যেখানে সফট মেটিরিয়াল দিয়ে স্ট্রাকচার রিপ্রোডিউস করা হত। এবং আমিই প্রথম ভারতের মধ্যে মডেল ডিফরমেশনে গবেষণা করি। আমি জিএসআই ছেড়ে যাদবপুরে জয়েন করি এইট্টি টু-তে, আর সুবীরবাবু রিটায়ার করেন ২০০০ সালে। ফলে, দীর্ঘ সময় ওঁর সান্নিধ্য পেয়েছি। আর শুধু যে জিওলজি শিখেছি, তা নয়, ওনার লিটারেচারের জ্ঞান ছিল অসম্ভব ভালো, ছবি আঁকায় প্রচুর জ্ঞান ছিল। ফিল্ডে গিয়েও ওঁর সঙ্গে যে আলোচনা হত, ইট ওয়াজ সো এনরিচিং। উনি বলতে গেলে প্রকৃত অর্থেই আমার ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড। উনি খুব মুখচোরা ছিলেন। আমি তো খুবই বিদেশি মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। সেখানে আমাকে লোকে জিজ্ঞাসা করত, উনি তো বাইরে আসেন না, ওখানে বসে বসেই কীভাবে এত উচ্চমানের গবেষণা করে যাচ্ছেন। মানুষের খুব কৌতূহল ছিল ওনাকে নিয়ে। আমি পোস্ট-ডক্টরেটও করেছি খুব নামী মানুষদের কাছে। ইংল্যান্ডে জেনেট ওয়াটসন আর জন র্যামসে এবং সুইডেনে হ্যান্স র্যামবার্গ। র্যামসে আবার খুব জমাটি লোক ছিলেন। ওঁর সত্তর বছরের জন্মদিনে ওরা স্যুইজারল্যান্ডে র্যামসের পুরনো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করেছিল, সেখানে উনি নিজে আমার নাম রেকমেন্ড করেছিলেন বলে ওরা আমার সব খরচাপাতি দিয়েছিল। সারা পৃথিবী থেকে মোট কুড়িজন অধ্যাপককে ওরা ডেকেছিল। আমাকে ‘সু’ বলে ডাকতেন, অনেক সময় নিজের হাতে করা পুরনো ম্যাপ অন্য কাউকে দিতেন না, আমাকে দিয়ে যেতেন। ভিসা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, র্যামসেকে কতবার ফোন করেছি, সময়ের পার্থক্য আছে, হয়তো অসময়েই ফোন করছি, তা সত্ত্বেও উনি সামান্যতম বিরক্ত না হয়ে বলছেন, কোনোরকম অসুবিধা হলে জানাতে দ্বিধা করো না, আমাকে ফোন করো। আশি বছরের জন্মদিনের সময়েও উনি আসতে লিখেছিলেন, কিন্তু আমার অসুবিধা হওয়ায় যেতে পারিনি। তবে সুবীরবাবু ও র্যামসে, দুজনেই খুব সহজ ভাষায় বিষয়টা বুঝিয়ে দিতে পারতেন। একটু কমজোরি স্টুডেন্ট হলেও তাকে বোঝাতে ওনারা অসুবিধায় পড়তেন না। প্রচুর ধৈর্য ছিল ওঁদের। র্যামবার্গ আবার অতটা ওরকম ছিলেন না। উনি বেশি বোঝাতে পারতেন না। তবে এটা তো পুরোপুরিই যার যার নিজস্বতা।
(জেনেট ওয়াটসন ও জন র্যামসে দুজনেই লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো। প্রথম মহিলা হিসেবে জিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিল জেনেট। স্ট্রাকচারাল জিওলজি পড়তে গেলে যে ফোল্ড সম্পর্কে অবহিত হতে হয়, সেই ফোল্ডের শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন জন র্যামসে, যাকে ‘র্যামসে’স ক্লাসিফিকেশন অফ ফোল্ডস’ বলা হয়ে থাকে। হ্যান্স র্যামবার্গ ছিলেন গবেষণার ক্ষেত্রে টেকটনিক মডেলিং প্রযুক্তির পুরোধা। র্যামবার্গাইট মিনারেলটির নামকরণ হয়েছে তাঁর নামে।)
আরও পড়ুন
‘২১ ফেব্রুয়ারি নিয়ে আমরা গর্বিত, অথচ ছেলেমেয়েদের ভর্তি করি ইংরাজি মিডিয়ামে’
আপনি এত দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত, এত কিংবদন্তি ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনার কাজ, সাক্ষাৎ। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই গবেষণা-বিমুখী, আবার অনেকেই গবেষণা করতে চেয়েও মনোমত স্বাচ্ছন্দ্য পায় না, তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কী বলবেন?
এক্ষেত্রে আমি একটু অন্যভাবে বলব, যে, হ্যাপিনেস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং ইন দ্য লাইফ। যার যা করতে ভালো লাগে, সে সেটাই করুক, সেটা নিয়েই পড়ে থাকুক। যদি রিসার্চ করতে ভালো লাগে, শুধুমাত্র সেই ভাবলেই রিসার্চে এস, আর কিছু ভেবো না। চাকরি না পেলে রিসার্চ করতে আসা চিরকালই ছিল, আমাদের সময়েও ছিল, আমরা বলতাম ‘স্টপ-গ্যাপ রিসার্চ’। আমার ছাত্রছাত্রীরাও কিছু সেরকম ছিল, তাদেরও অত সিরিয়াসলি নিতাম না। এই মানসিকতাটা ভারতে একটু বেশিই কারণ, পর্যাপ্ত চাকরির অভাব। আর রিসার্চ ফেলোশিপ ঠিকমতো না আসা তো আরেক স্টোরি। আমাদের সময়েও তাই ছিল, এখনও তাই, কোনো পরিবর্তন নেই। রিসার্চ-সাপোর্টের ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের মতো এত দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকার বোধহয় আর নেই। পঞ্চাশ বছর ধরেই তো দেখছি, ন’মাস-দশ মাস পর টাকা পাঠায়। তার মধ্যেও সত্যিই যারা রিসার্চটা মন দিয়ে করে, তা তো সত্যিই প্রশংসার।