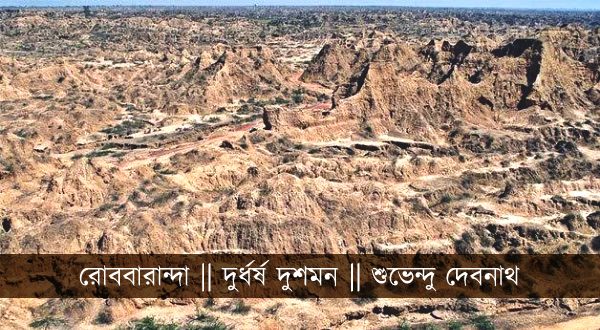(ভোট চলছে বঙ্গে। কিছুকাল আগে পর্যন্ত এঁদের সরব উপস্থিতি ব্যতিরেকে বঙ্গে ভোট-রঙ্গের কথা ভাবাই যেত না। তাঁরা নেই, আবার আছেনও, আমার স্মৃতি ও সত্তায়। তেমনই কয়েকজন বঙ্গ-রাজনীতির মহারথীদের নিয়ে আমার এই সিরিজ। প্রথমে অনিল বিশ্বাস।)
১৯৬২ সাল থেকে ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেও অনিল বিশ্বাস দলের সক্রিয় সদস্য হয়েছিলেন তিন বছর পরে৷ ঠিক তার আগের বছরে অবিভক্ত সিপিআইয়ে ভাঙন ধরেছে, নতুন দল হিসেবে সিপিএম সবে অঙ্কুর মেলছে৷ তারও তেরো বছর পরে, ১৯৭৮ সালে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার এক বছরের মধ্যে তাঁকে রাজ্য কমিটির সদস্য করা হয়, ১৯৮২-তে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর৷ ১৯৮৫-তে তিনি মনোনীত হন দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে, ১৯৯৮-এ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ার পরে পলিটব্যুরোয়৷ করিমপুরের এক অখ্যাত গ্রাম থেকে শৈশব, কৈশোর, যৌবনের যাবতীয় ক্লেশ এবং অনটনকে উপেক্ষা করে সিপিএমের মতো শৃঙ্খলাপরায়ণ, রেজিমেন্টেড দলে অনিলদার এই যে উত্থান তা অনেকটা রূপকথার গপ্পের মতোই৷ বিশেষ করে বিমান বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পারিবারিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তুলনা করলে সম্যক বোঝা যায় তাঁর ব্যক্তিজীবনের লড়াইটা কতটা কঠিন ও দুর্লঙ্ঘ ছিল৷
কমিউনিস্টদের মধ্যে তাত্ত্বিক নেতা বলতে যা বোঝায়, অনিলদাকে অবশ্যই সেই গোত্রে ফেলা যাবে না৷ জীবৎকালে এই মধ্য-মেধার পরিশ্রমী মানুষটি কোনোদিন তেমন দাবিও করেননি৷ তাঁর প্রধান মূলধন ছিল বরফ-শীতল ঠান্ডা মস্তিষ্ক যেখানে নানা সুবুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধি একই সঙ্গে একই ছন্দে খেলা করত, ব্যক্তিগত স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার তাগিদে ততটা নয় যতটা দলের ঐক্য রক্ষা করতে৷ বিমান বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো তাঁকে কোনোদিন মাথা গরম করতে দেখিনি, পা দিতে দেখিনি সাংবাদিকদের কোনো প্ররোচনায়, মুখ ফসকেও প্রকাশ্যে তিনি কদাপি এমন কোনো মন্তব্য করেননি যা নিয়ে পরে মিডিয়া বিতর্ক করার সুযোগ পায়৷ ব্যক্তিগত স্তরেও তাঁর সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর পরে ঘনিষ্ঠতা সম্ভব ছিল বলে আমার মনে হয়নি, স্বাভাবিক সৌজন্যের বাইরে তিনি বড় একটা কারও সঙ্গে মাখামাখি করতেন না, দলীয় কমরেডদের বাইরে তো নয়ই৷ তাঁর স্বভাবটা ছিল চাপা, কিছুটা মুখচোরাই, নাকি স্বরে ধীর লয়ে নিচু গ্রামে কথা বলতেন, উচ্চারণে স্পষ্ট হত সীমান্ত বাংলায় বড় হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপট৷ বাবা-বাছা করে জেলায় জেলায় দলের বিবদমান গোষ্ঠপতিদের একসঙ্গে রাখার কঠিন কাজটিতে এমন ঠান্ডা মাথার বড় প্রয়োজন ছিল৷ ঠিক যেমন বিরোধীদের হঠাৎ হঠাৎ অপ্রস্তুত করে দেওয়া বা মোক্ষম প্যাঁচে ফেলার জন্যও প্রয়োজন ছিল মগজাস্ত্রের৷ আমরা অনেকেই তাঁকে আলিমুদ্দিনের ‘চাণক্য’ বলে রসিকতা করতাম৷ সঙ্কটের সময় কূট-বুদ্ধি দিয়ে পরিকল্পনা রচনা করা এবং তা রূপায়নের জন্য নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে অনিল বিশ্বাসের সম্ভবত কোনো জুড়ি ছিল না৷
ব্যক্তিগতভাবে আমার অন্তত বারেবারেই মনে হত সব কিছুর ঊর্ধ্বে নিজের সাংবাদিক পরিচয়টি নিয়েই একটা চাপা গর্ববোধ ছিল তাঁর৷ হয়তো সেটা সম্পূর্ণ অকারণেও নয়৷ ১৯৬৫ থেকে ১৯৯৮, একাদিক্রমে টানা তেত্রিশটি বছর তিনি দলের মুখপত্র গণশক্তিতে সাংবাদিকতা করেছেন, তার মধ্যে পনেরোটি বছর (১৯৮৩ থেকে ১৯৯৮) ছিলেন তার সম্পাদক৷ তাঁর নেতৃত্বেই দলীয় মুখপত্রটির কলেবর, প্রচার ও প্রসার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল বাণিজ্যিক বাস্তবতাকে শিরোধার্য করেই৷ খবরের কাগজের ব্যবসার প্রাসঙ্গিক সব কিছু তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন, কলকাতার কোন কাগজ কত বিক্রি হয় সর্বদা এই তথ্যগুলি থাকত তাঁর নখদর্পণে৷ মাঝে মাঝেই ইয়ার্কি মেরে অনিলদাকে বলতাম, ‘সিপিএমের চাকরি গেলে আপনার কুছ পরোয়া নেই, যে কোনও বুর্জোয়া কাগজ লাল কার্পেট পেতে আপনাকে সার্কুলেশন ম্যানেজার করে নিয়ে নেবে৷’ পরে করিমপুরে গিয়ে দেখেছি, অনিলদার সহোদরও যুক্ত ছিলেন কাগজের সার্কুলেশনের ব্যবসায়৷
আরও পড়ুন
ভোট আসতে যাবতীয় দুশ্চিন্তা ঘুচে গেল অনিলদার
অনিলদার সাংবাদিকতার সঙ্গে আমাদের সাংবাদিকতার কোনো মিল ছিল না, থাকার কথাও নয়৷ তবু তাঁর সম্পাদিত মুখপত্রটি আমাদের কাছে ছিল অবশ্যপাঠ্য৷ কোন বিষয়ে সিপিএমের দলীয় নীতি কোন খাতে বইছে, কোনো বিষয়ে দলের অন্দরে একাধিক মত মাথা চাড়া দিচ্ছে কি না, কিংবা মুখপত্রে কোন বিষয়টি তুলনায় বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে, এ সব জরুরি বিষয়গুলি বোঝার জন্য গণশক্তি পড়াটা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ত৷ ‘বিটুইন দ্য লাইনস’-এ ধরা পড়ত পার্টির মতিগতি, সাদা চোখে ধরা পড়ত না৷ অনুচ্চারিত তথ্য বা ভাষ্য নিয়েই থাকত আমাদের বেশি কৌতূহল৷
সে সময় সিপিএমে এত কড়া শৃঙ্খলা বা অনুশাসন ছিল যে নেতাদের সঙ্গে ভাব পাতিয়েও খবর বের করা যেত না সচরাচর৷ দলীয় মুখপাত্রের বাইরে পারতপক্ষে কেউ মুখ খুলতেন না, সবার মুখে একটিই গদ উচ্চারিত হত - আমি নয় ভাই যা বলার পার্টিই বলবে৷ আর তা না হলে অবধারিত গালাগালি, ‘আপনাদের সঙ্গে কথা বলে কী লাভ? আমরা যা বলব তা তো আপনারা লিখবেন না, মালিক যা বলবে সেটাই লিখবেন৷’ প্রথম প্রথম রাগ হত কমরেডদের দাঁত-খিঁচুনি দেখে৷ পরে ধীরে ধীরে গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল যদিও এই বৈরিতার মর্ম বিশেষ একটা বুঝতে পারতাম না৷ অনেক সময় মনে হত, লোকগুলোর কী খবরের কাগজ কীভাবে চলে সে সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই নেই নাকি ইচ্ছে করে সব জেনেশুনেই এ সব কথা বলে? কালে কালে সিপিএমের সেই দুর্ভেদ্য-আঁটোসাঁটো দলীয় শৃঙ্খলা অনেকটাই শিথিল হয়ে গিয়েছে, ২০১১-য় দল ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে তো একেবারেই৷ সিপিএমের ভিতরের খবর বের করা এখন তৃণমূলের খবর জানার চেয়ে সামান্য কঠিন!
আরও পড়ুন
যাব যাব করেও সুভাষ থেকে গেলেন
এ সবই অবশ্য প্রাক টেলিভিশন পর্বের কথা৷ কলকাতায় চব্বিশ ঘণ্টার বাংলা নিউজ চ্যানেল ভালো করে গেঁড়ে বসার আগেই অনিলদা চলে গিয়েছিলেন৷ ফলে টেলিভিশনকে কী করে ব্যবহার করতে হয় বা টেলিভিশনের জমানায় কীভাবে রাজনীতি করতে হয়, অনিলদা তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তারই অবকাশ পাননি৷ তাঁদের যাবতীয় ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিল কলকাতা থেকে প্রকাশিত চারটি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে৷ কাগজকে গালাগাল না দিয়ে সেকালে কমরেডরা জলপান করতেন না, প্রতিটি জনসভায় হয় কাগজের নাম করে বা না করে তাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হত৷ ভাবখানা এমন যেন কংগ্রেস নয় সংবাদপত্রই তাঁদের একমাত্র প্রতিপক্ষ৷ সিপিএমের সভা করতে যাওয়া বুর্জোয়া এবং বাজারি কাগজের রিপোর্টারদের চড়-থাপ্পড় খাওয়ার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতে হত অনেক সময়৷ যদিও বাম-জমানায় প্রকাশ্যে রিপোর্টার পেটানোর ঘটনা বিশেষ একটা ঘটেনি৷
খবরের কাগজকে খামোখা গালাগাল দিয়ে সিপিএম নেতাদের সত্যিই কতটা লাভ হত আমি বুঝতে পারতাম না৷ এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গে খবরের কাগজের সংখ্যা এবং বিক্রি দেশের অন্য রাজ্যের তুলনায় নেহাতই কম৷ সত্তর কিংবা আশির দশকে ছবিটা ছিল আরও মলিন৷ রাজ্যের সাত-সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে খবরের কাগজ বিক্রি হত বড় জোর দশ লাখ৷ অর্থাৎ রাজ্যের জনমতকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করার জায়গায় খবরের কাগজ এ রাজ্যে কোনো দিনই ছিল না, এখনও নেই৷ তার চেয়েও বড় কথা খবরের কাগজ পড়ে যদি রাজ্যবাসী শাসক নির্বাচিত করতেন তাহলে বামফ্রন্ট কোনো দিন ক্ষমতায় আসতে পারত না কিংবা একবার আসার পরে টানা চৌত্রিশ বছর চালিয়ে যেতে পারত না রাজ্যপাট৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে বামেরা দীর্ঘদিন যাবৎ এ রাজ্যে সংবাদপত্রকে বোধহয় প্রাপ্যের অতিরিক্ত গুরুত্বই দিয়ে এসেছেন৷ তাতে ওঁদের যতটা লাভ হয়েছে তার চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছি আমরা৷ শাসকের ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার মুখে আমরা যে যার মতো করে কলার তুলে ঘুরে বেড়িয়েছি৷
আরও পড়ুন
অনিল বিশ্বাস : বঙ্গ রাজনীতির চাণক্য
সংবাদপত্রকে নিয়ম করে গাল দিলেও ব্যক্তি সাংবাদিকদের অনেকের সঙ্গেই কমিউনিস্ট নেতাদের ভালো সম্পর্ক ছিল৷ অন্যভাবে বলতে গেলে মালিকের দাস হিসেবে দেখে তাঁরা আমাদের যেন একটু বাড়তি করুণাই করতেন৷ দু’এক সময় রক্ষাও করেছেন৷ যেমন আমার এক প্রয়াত অগ্রজ পরিমল ভট্টাচার্যের মুখে শুনেছিলাম এমনই একটি ঘটনার কথা৷ হাওড়ার কোনো একটি জনসভায় পরিমলদার কাগজের বিরুদ্ধে জ্যোতি বসু এমন গালাগাল দিলেন যে জনতার গা গরম হয়ে গেল৷ খোঁজ শুরু হয়ে গেল, সেই কাগজের কোনো প্রতিনিধি ওই জনসভায় আছেন কি না৷ জনতার মুড বুঝতে পেরে লোক মারফৎ পরিমলদাকে জ্যোতিবাবু ডেকে নিলেন মঞ্চে৷ বললেন, ‘আপনি একেবারে মঞ্চের পাশে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকুন৷ মিটিং শেষ হলেই আমার সঙ্গে গাড়িতে উঠে পড়বেন৷ ’ হলও তাই৷ পরিমলদাকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে জ্যোতিবাবু হাওড়া ব্রিজ পার করে দিলেন৷
কেবল রাজনৈতিক সমাবেশে নেতাদের গালাগালেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকত না, সিপিএমের দলীয় মুখপাত্রেও কাগজের নাম করে নানা চটূল কিন্তু বিরূপ টীকা-টিপ্পনি থাকত৷ অনেক সময় থাকত ব্যক্তিগত আক্রমণও৷ তবে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের নামটি এড়িয়ে যাওয়া হত অতি সন্তর্পণে৷ সে সময় মনে হত বাজারি কাগজের খবর খণ্ডন করা বা মতামতকে বিদ্রুপ করাটাই সিপিএমের মুখপাত্রের অন্যতম কাজ৷ হামেশা গালাগাল দেওয়া হত আমাকেও৷ বেশ মজা লাগত, ফোকটে বাড়তি প্রচারটুকু পেয়ে যাওয়ার জন্য মনে মনে অনিলদাকে কৃতজ্ঞতা জানাতাম৷
আরও পড়ুন
জোট-ঘোঁট-ভোট (১)
অবশ্য সংবাদ মাধ্যম শাসকের প্রতিপক্ষের অবস্থানে থাকাটা গণতন্ত্রের পক্ষে অতি স্বাস্থ্যকর এবং প্রত্যাশিত৷
Powered by Froala Editor