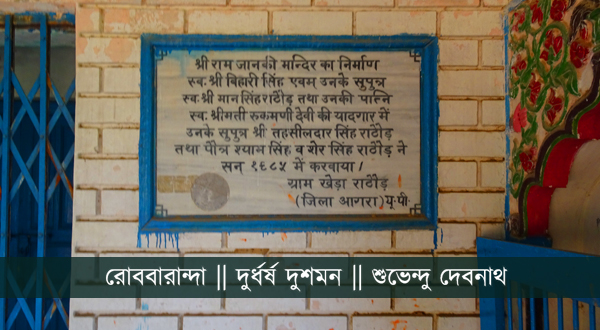সময়ভ্রমণ – ৫
আগের পর্বে
ইদানীং পেশকে বর্ষাকাল ছাড়া রং ধরেনা তেমন। কারণ সেগুন গাছ মাটি থেকে এতটাই জল টানে যে ঘাস, লতা, গুল্ম অন্যসময় জন্মাতে পারে না। সেই পেশকের বিখ্যাত কাঠবাংলোটাও আর নেই। শুধু পেশকের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক অনেক রহস্য অভিযানের কথা। আরও একটু ওপরে উঠলে লামাহাটা। ভুটিয়াদের পুরনো গ্রাম। উনিশ শতকের শেষেই দার্জিলিং অবধি রেলপথ তৈরি হয় যায়। তাড়িয়ে দেওয়া হয় লেপচা এবং ভুটিয়াদের। শুরু হয় ব্রিটিশ শক্তির তত্ত্বাবধানে বননিধন। স্বাধীনতার পরেও হিমালয়ের আদি বনভূমি উচ্ছেদ করে বসা হয়েছিল কৃত্রিম ধুপি। এক আধিকারিক পরে জানিয়েছিলেন আফসোসের কথা। তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় ধরা আছে সেই পুরনো পাহাড়ি দৃশ্য। আছে নীলপাহাড়ের আবিষ্কার। সে আরেক গল্প।
লামাহাটার পাইনবাগান ছেড়ে পেশক পথ ধরে এগুতে থাকলে ডানহাতি একাধিক রাস্তা খাড়া উৎরাই বেয়ে বহু, বহু নিচে রংগু নদীর দিকে নেমেছে। রংগুর আসল নাম কি ছিল কে জানে? রঙন্যু বা রঙ-ইয়্য নামের চল ছিল একসময়। দার্জিলিং পাহাড় যখন সিকিম দেশের অংশ ছিল, তার একটা সীমানা ছিল রংগু নদীর গিরিখাত, মাইল চারেক লম্বা, চার হাজার ফুট গভীর। রংগু বা রঙনু বা রঙ-ইয়্য, যে নদী খাড়া আর সোজা যায়, গিয়ে মিশেছে রঙ-ন্যিতে বা রঙ্গিতে। এদিক দিয়ে না এসে রংগুর ওপারের দার্জিলিং পাহাড় দিয়েও এ অঞ্চলে নামা যায়। দুদিকের পাহাড়ি ঢালে অসংখ্য চাবাগান, একদম নিচের দিকে আর ওপরের দিকে বন। এখন গাড়ি যাবার পথ হয়েছে কিছু কিছু জায়গায়, অবশ্য সেসব খুব সরু, আর প্রায়ই খুব ভেঙেচুরে থাকে। রংগু নদী অবধি যেতে হলে হাঁটতেই হয়।
এদিক থেকে অর্থাৎ পেশক পথের দিক থেকে তাকদা বাগান আর গ্লেনবার্ন বাগান পর্যন্ত গেছে যে সরু উৎরাই পথ, সে পথ ধরে এগোলে রংগু উপত্যকা যে কতটা সুন্দর তা বোঝা যায়। পথের পাশের ধুপিবাগানের ফাঁকে ফাঁকে ওক-রডোডেনড্রন, ফার্ন, যে ঋতুতেই যাওয়া যাক, নাম না জানা অসংখ্য উজ্জ্বল বনফুল, হলুদ, লাল, গাঢ় লাল, সাদা, গোলাপি, নীলচে, বেগুনি। বন ছাড়ালেই যতদূর চোখ যায় পাহাড়ি ঢাল ঢেকে চা-বাগান, আরো নিচে বিন্দুবৎ গ্রাম, আরো আরো নিচে বনে ঢাকা নদী। বাঁদিক ঘেঁষে ওপরের দিকে তাকালে নীল আকাশ থেকে খাড়া নেমে এসেছে টাইগার হিলের সবুজ পাহাড়। ডানদিকে তাকালেই দিগন্ত জুড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা, তার ডানদিকে বাঁদিকে বরফের পাহাড়ের সারি চলে গেছে ভুটান আর পূর্ব নেপাল পর্যন্ত। এ ছবি সারা বছরের নয়। অক্টোবরে বর্ষাশেষ, তারপর নভেম্বর আর ডিসেম্বরের প্রথম দুতিন সপ্তাহ পাহাড় ছেয়ে রোদ ঝরতে থাকে, অন্য গিরিশিখর নাই দেখা যাক, কাঞ্চনজঙ্ঘা সারাদিন, এমন কি রাতেও চোখের সামনে, সকালে গোলাপি-লাল, দুপুরে চোখ ঝলসানো সাদা, বিকেলে গোধূলিতে আবার লালচে-গোলাপি, সন্ধ্যারাতে ঈষৎ হলদেটে, ছায়াময়। বছরের অন্য সময়, পেশক পথ থেকে ওপারের দার্জিলিং পাহাড়ের গিরিশিরা মেঘে ঢেকে যায় কিম্বা আবছা হয়ে আসে, কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মেলে কদাচিৎ। বর্ষার শুরুতে, মে-জুন মাসে, আর শেষের দিকটায়, সেপ্টেম্বরে, সমস্ত এলাকাটা দিয়ে মেঘ ওঠে আর নামে, চরাচর ধুয়ে জল পড়তে থাকে কখনো-কখনো। হঠাৎ মেঘ সরে যায়, রোদ এসে পড়ে চা-বাগানের কালচে-সবুজে, গ্রামের বাড়ির টিনের চালের লালে, টাইগার হিলের মাথা থেকে নিচের দিকে আসা, আর রংগু থেকে ওপরে উঠতে থাকা মেঘের তীব্র সাদায়।
রংগু উপত্যকায় পৌঁছনোর আরো নানা পথ আছে। পেশক পথ ধরে এগুলে রাস্তার ওপরের ছ’মিল বা ছ’মাইল গ্রামের অগোছালো, ঘিঞ্জি বসতি। ছ’মাইলের পর আবার বন। তারপরে তিন মাইল। তিন মাইলের পর গদ্দিখান। ছোট বড় গ্রাম। এই সব জায়গাগুলো থেকেই পরিষ্কার রোদের দিনে দার্জিলিং পাহাড়ের মাথায় অবারিত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা সম্ভব। তিন মাইল গ্রাম থেকে একটা পুরনো সরু পথ রঙ্গারুন বনের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে নেমে গেছে রঙ্গারুন বাগান হয়ে রংগু নদীর দিকে, আর একটা পথ পয়তিসে পারমেন ফারেস বস্তির পাশ দিয়ে দাওয়াইপানি গ্রামের ভোটেবস্তি অবধি গেছে। সবকটা পথই এখনও নিঃঝুম, নিজের মতো করে সুন্দর। এসবের কথা পরে হবে। আপাতত গন্তব্য নীলপাহাড়ি। সেটা কোথায়?
তিস্তা উপত্যকার তিস্তা ভ্যালি পথের কথা বলেছি। সিকিমের দিকে মুখ করে নদী ছেড়ে বাঁদিকের পাহাড়ে চড়া যায় এই পথ ধরে। কালিম্পং আর সিকিম যাতায়াতের পথে বাঁদিকের সরু পথ চোখে পড়ত। তার গোড়ায় হলদে রং করা একটা পাথরের ফলকে তির চিহ্ন দিয়ে লেখা থাকতো, তিস্তা ভ্যালি রোড। তিস্তা নদী ছেড়ে উঠে যাচ্ছি ওপরের পাহাড়ে, অথচ পথের নাম তিস্তা ভ্যালি রোড, কেন? সে অর্থে নিচের বড় রাস্তার নামই তো হওয়া উচিত তিস্তা ভ্যালি। (পুরোনো বইপত্র হাতড়ে দেখলাম, নিচের বড় রাস্তাটাকেই অন্তত ১৯৪৭ অবধি তিস্তা ভ্যালি রোড বলা হত। সৈন্যসামন্ত যুদ্ধবিগ্রহ আর জাতীয় রাজমার্গ ইত্যাদির দাপটে সে নাম চাপা পড়ে গেছে নিশ্চয়)। নামের নানারকম হয়, রকমফের থাকে, পুরোনো নামের ওপর নতুন নাম চাপে হামেশা, এমনকি নামেরও নাম হয়, সেটা য়্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড যারা পড়েছে তারা প্রত্যেকে জানে।
আরও পড়ুন
পেশকের পথ ধরে
নামের কথা, নামের ইতিহাসের কথা, নামের নামের কথা মুলতুবি থাক। তিস্তা ভ্যালি রোড ধরে অনেকটা উঠে গিয়ে পাওয়া যাবে রংলি রঙলিওট বাগান, লেপচা লোককথায় বর্ণিত ইতিহাস অনুযায়ী, ক্রুদ্ধ রঙ-ন্যিয়োর জল যে পর্যন্ত উঠেছিল। এই লোককথাটার দুটো আলাদা বয়ান আছে। মূল গল্পটা এক, দুই নদীর বিয়ে। ডেভিড ম্যাকডোনাল্ড ও বুভয়া-স্টকস এর সংগৃহীত যে গল্পটা আমি বলেছি, সেটায় রঙ-ন্যিয়ো অর্থাৎ তিস্তা পুরুষ, সে রেগে গিয়ে পাহাড়বন ডুবিয়ে রংলি রঙলিওট অবধি পৌঁছে গিয়েছিল। অন্য বয়ানটা রিসলে সাহেবের বিখ্যাত সিকিম গ্যাজেটিয়ারে আছে, তার আগে ওয়াডেলের লেখাতেও। এই বয়ান অনুযায়ী রঙ-ন্যিয়ো পুরুষ নয় মেয়ে, অন্যদিকে রঙ-ন্যিত মানে রঙ্গিত পুরুষ, সেই-ই বেজায় রেগেমেগে রংলি রঙলিওট গিয়ে থেমেছিল। হয়তো এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, আদিতে নারী-পুরুষ বিভাজন ছিল না, যিনি নারী তিনিই অবস্থান্তরে বা ভিন্ন ইতিহাসে পুরুষ, অথবা একই শরীরে কখনো নারী কখনো পুরুষ। নারীবাদী, পরিবেশবাদী, কল্পবিজ্ঞান ও ফ্যান্টাসির অধুনা-প্রয়াত লেখক উরসুলা লে গুইনের একটা লেখায় এমন এক পৃথিবীর কথা আছে, যেখানে সমস্ত মানুষ একইসঙ্গে ছেলে ও মেয়ে, নারী ও পুরুষ। তন্ত্র ব্যাপারটা আদৌ কিছু জানি না, কিন্তু প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হিমালয় ভ্রমণ এবং তান্ত্রিকসঙ্গের উপভোগ্য বিবরণে পড়েছি সাচ্চা তান্ত্রিকেরা পুরুষ-প্রকৃতি(অর্থাৎ নারী) ভেদাভেদ করেন না, সৃষ্টির মূল যে প্রাণ, তিনি একাধারে নারী ও পুরুষ। ফলে হতে পারে, হতেই পারে, রঙ-ন্যিয়ো পুরুষ নয় মেয়ে, ওদিকে রঙ-ন্যিত মেয়ে নয় পুরুষ।
রঙ-ন্যিয়ো, কিম্বা রঙ-ন্যিত, কিম্বা রঙ-ন্যিয়ো-নিত যেখানে পৌঁছে থেমেছিল, সেই রংলি রংলিওট ছাড়িয়ে কিলোমিটার খানেক গেলেই তাকদা। প্রথমবার যখন যাই, ঘোর শীতকাল, সন্ধ্যা হব-হব, চাদ্দিকে থিক-থিক করছে কুয়াশা। কুয়াশার মধ্যে একটা সবুজ-লাল বোর্ড দেখে জানা গেল পথের বাঁদিকেই বিশাল কাচের ঘরের মধ্যে অর্কিড রাখা আছে। দার্জিলিং এর বট্যানিকাল গার্ডেনের বিখ্যাত অর্কিড-ঘর দেখেছি, সে তুলনাতেও তাকদার সংগ্রহ বিপুল, চমকপ্রদ। কিন্তু অর্কিড দেখে আরাম বনের ভিতরে, বনে না হলেও পুরনো গাছের গায়ে। এর পরেও দু চারবার গেছি, অর্কিডঘর ছাড়া তাকদায় কি আছে, আলাদা করে সেটা খুঁজে দেখবার কথা মনে হয়নি। সেটা যখন হল, তার আগে তাকদা এলাকার সঙ্গে, সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। জানা হয়ে গেছে, তাকদা বলতে একটাই জায়গা নয়, তাকদা চা-বাগানটা একদিকে, আর এখন যে তাকদার কথা হচ্ছে সেটা অন্যত্র, তারও দুটো টুকরো, একটা তাকদা খাসমহল, একদা তাকদা ক্যান্টনমেন্ট। ক্যান্টনমেন্ট? পুরোনো বইপত্র ঘেঁটে দেখা গেল, ১৯১০ নাগাদ ব্রিটিশরা পাহাড়বনের মাঝখানে একটা নতুন সেনাছাউনি চালু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার কিছু পরে সেখানে মিলিটারি লোকজনের বাস ছিল। ১৯২৬-এ নানান কারণে সেনাছাউনিটা উঠে যায়। ক্যান্টনমেন্ট হল যে জায়গাটা আগে পরিচিত ছিল হুম-লিংডিং বা হুম-তাকদা নামে। তাকদা নামের আরো জায়গা ছিল--বিদুর সিংয়ের তাকদা, পেমচন্দ ভুটিয়ার তাকদা। ইজারাদারের নামে জায়গার নাম। কোথাও জমি ইজারা নিয়ে কেউ গরু-ভেড়া চরাচ্ছে, কেউ প্রজা বসাচ্ছে। হুম-লিংডিং বা তাকদা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় গোর্খা সেনাবাহিনী সহ সায়েব অফিসারেরা খুঁটি গাড়লেন। সায়েবদের থাকার জন্য সায়েবি কায়দায় সুদৃশ্য বাংলো হল বনের ভিতরে, পাহাড়ের মাথায়। পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি সে সব বাংলোর কাঁচের জানলা, কাঠের সিঁড়ি, সামনে প্রশস্ত লন। কোনটা একতলা, কোনটা দোতলা। বাংলোগুলো নাম দিয়ে চেনা যেত, ২ নং, ১২ নং, ৮ নং।
আরও পড়ুন
লেপচা-দুনিয়ায়
ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে সায়েবরা বিদায় নিলেন। তাদের পাথরের-কাঠের, কাঁচের শার্সি-বসানো, ঘরে ঘরে গনগনে ফায়ারপ্লেস আর বাড়ির মাথায় নানান চেহারার চিমনি-ওলা বাংলোগুলো থেকে গেল, বনের ভিতরে, পাহাড়ি টিলায়। সেনাছাউনির কিছু জমি চলে গেল রংলি রঙলিওট চা-বাগানে।
এরপর থেকে কি হল সে ইতিহাসটা কিম্বা গল্পটা খুঁজে পাওয়া কঠিন। স্থানীয় বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছি, পরে সরকারি বনবিভাগের পুরনো কাগজপত্রেও পড়েছি, কলকাতার অবস্থাপন্ন বাঙালিরা সে সব বাংলো কিনে নিয়েছিলেন। সে সময় দার্জিলিং, কালিম্পং, কারসিয়াং, সর্বত্র বাঙালিদের বাস ছিল। কেউ কেউ ছুটি কাটাতে বা শরীর সারাতে আসতেন। বাকিরা ওখানেই থাকতেন। সেকালে সায়েবদের রাজত্ব যে শেষ হতে পারে, সেটা ভাবা দুষ্কর ছিল। ফলে সায়েবদের জায়গায় সায়েবদের মতো করে থাকবার একটা মাহাত্ম্য ছিল। রাজা-জমিদারেরা আর শিক্ষিত বাঙালিরা পাহাড়চূড়ায় সায়েবদের মতো থাকবার জন্য অসংখ্য ভিলা, বাংলো, কটেজ, এসব বানিয়েছিলেন, অথবা সায়েববাড়ি কিনে নিয়েছিলেন। তাকদা শহরের কাছাকাছি নয়, দার্জিলিং বা ঘুম থেকে পৌঁছবার গাড়ির পথও তৈরি হয়নি, অথচ কলকাতার মানুষেরা এসে কেন এখানে ডেরা গাড়লেন, বোঝা মুশকিল।
আরও পড়ুন
তিস্তা বা রঙ-ন্যিয়োর গল্প
আমি যে সময় তাগদার সায়েববাড়িগুলো ভালো করে দেখি, সেগুলোর বেশির ভাগেরই করুণ দশা। দেয়াল ধসে পড়ছে, মেঝের কাঠের পাঠাতন পচে গেছে, ছাদ ফুটো, তার ওপর প্লাস্টিক টাসটিক চাপিয়ে ইঁট চাপা দিয়ে জল আটকানোর ব্যর্থ চেষ্টা। দু তিনটে বাড়ি ভালো অবস্থায় ছিল। তার মধ্যে একটাতে আমার বন্ধু ডিপি লামা থাকতেন। তাঁর অনুগ্রহে সে বাড়ির দোতলায়, কাঁচের শার্সি বসানো ফায়ারপ্লেস ওলা শোবার ঘরে বেশ কিছু রাত্রি কেটেছিল। বাইরের লন পেরিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকেই যে বসবার জায়গা, সেখানে ফায়ারপ্লেসের ওপরে একটা পুরনো সাদা-কালো ছবি রাখা থাকত। সে ছবিটায় এক দঙ্গল সায়েবদের মাঝখানে এক বাঙালি দম্পতি হাসি হাসি মুখে বসে আছেন। লামাদা ওই ছবিটাকে, আর বাড়িটাকেও খুব যত্নে রাখতেন। ছবিটা দেখিয়ে বলতেন, ওই দেখুন, মিঃ আর মিসেস রায়, এই বাড়ির আসল মালিক। খুব ভালো লোক ছিলেন। রায় সাহেব মারা গেলেন, মিসেস রায় আসতে পারেন না। ওঁরা যখন থাকতেন না, বাড়িটা আমি দেখাশোনা করতাম। মিসেস রায় বললেন, বাড়িটা আমি কি করব, তুমি নেবে? আমি নিয়ে নিলাম। এত ভালো বাড়ি।
রায় দম্পতি ছবিতে যেখানে বসেছিলেন, সে জায়গাটা তাকদা ক্লাব। আমি যখন দেখি, সেটা পোড়ো বাড়ি, কিন্তু দেয়াল মেঝে এসব ছিল। বাড়ির সামনের বিরাট মাঠে একটা সাইনবোর্ড লাগানো ছিল, এই সম্পত্তির মালিক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট বা আইএসআই। পরে সে বাড়ি(তার তখন শেষ অবস্থা), জমি সব বনবিভাগ নিয়ে নেয়। নিয়ে ট্যুরিস্ট রাখার জন্য 'হেরিটেজ' বাংলো তৈরি হয়। দ্বিতীয় গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন চলাকালীন সে বাংলোয় আগুন লাগে। শোনা যায় যে ওই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ একজন নেতা সেই আগুনের পিছনে ছিলেন। বাংলো পোড়ানোর পর আবার তৈরি হলে সে কাজের ঠিকে পাবেন বলে। পেয়েছিলেন কিনা জানা নেই, তবে ক্লাব থেকে কিছু দূরে সোনপুর হাউস বলে একটা পুরো বাড়ি দখল করে তিনি অন্য একটি হেরিটেজ থাকার জায়গা বানান। তাগদার পুরনো বাংলোগুলোর ভিতরে অনেকগুলোতেই এখন হেরিটেজ চলছে। লামাদার বাড়িটাতে কি হচ্ছে জানি না, উনি মারা গেছেন বেশ কিছুদিন হল। ২০০৮-৯ নাগাদ, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের তখন হইহই কান্ড, উনি আমাকে বললেন, বলছি যে আপনি এখন না এলেই ভালো, অবস্থা ভালো না, আমাকে এরা ভয় দেখাচ্ছে। উনি সেসময় ঘিসিং এর দল করতেন, সে দলের সমর্থকদের প্রত্যেক বাড়িতে গুরুং দলের পতাকা লাগাতে বলা হয়েছিল।
আরও পড়ুন
মরে-যাওয়া মাঠের ওপর অলৌকিক কালো সারসের মতো নেমে এসো, মেঘ
যে কদিন সে বাড়িতে ছিলাম, সেই স্মৃতি এখনো অম্লান সজীব, বসন্তে ইতস্তত ভেসে বেড়ানো শিমূল তুলোর রোঁয়ার মতো হালকা। তিস্তা ভ্যালি রোডের ধারে বাড়িটা, সামনের বারান্দা থেকে অর্কিডের থোকা ঝুলতো, সামনের লনে বিশাল গাছ-ঢেঁকি, মানে ট্রি-ফার্ন। ওপরের ঘর থেকে জানলার কাঁচ দিয়ে বাইরে তাকালে দেখা যেত, পাহাড়বন ভেঙে মেঘের দল নেমে আসছে, জানলা বন্ধ না করলে কুয়াশার কুঁচি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে বিছানা ভিজিয়ে দেবে। নিজের সৌভাগ্য অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেব বলে ওই বাড়ির দুটো ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম। লামাদাকে উৎসাহিত করেছিলাম তাকদায় বাইরের লোকেদের থাকবার মতো ছোট খাটো একটা আস্তানা করতে। এত ভালো জায়গাটা, লোকে দেখবে না, জানবে না? কেন যে ওই হুজুগ তুলেছিলাম? দ্রুত হেরিটেজওয়ালা পর্যটনব্যবসা ঢুকে এসে পুরো তাকদা ভরিয়ে দিলো। নেটে গিয়ে তাকদার খোঁজ করলে শুধু হেরিটেজ বাংলোর কথা পাওয়া যায়। অন্য কিচ্ছু নেই।
অথচ নীলপাহাড়ির খোঁজ করতে করতে ওই নেট থেকেই এক অপ্রত্যাশিত সন্ধান মিলেছিল একদা। এক বাঙালি মেয়ের ইংরেজিতে লেখা ব্লগ। সেসময় সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম চলছে, মেয়েটি যাদবপুরের ছাত্র বা গবেষক, বেশির ভাগ লেখাই সেসব নিয়ে। তার মাঝখানে একটা লেখায় মেয়েটির পরিবারের, তাদের পাহাড়ের বাড়ির কথা বলা ছিল। পারিবারিক পাহাড়ের বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে মেয়েটি তাকদায় পৌঁছে গিয়েছিল, চড়াই ভেঙে সবচাইতে উঁচু বাড়িটায় উঠেছিল। সে বাড়িতে তখন তিব্বতি বৌদ্ধবাদ শিক্ষার একটা স্কুল চলে। নিচে তাকালে একদম তিস্তার সমতল অবধি চোখ চলে যায়, আর রংলি রঙলিওট বাগান। সামনে পাহাড়জঙ্গল। সে বাড়িটাতে পরে আমিও গিয়েছি। তাকদা বা হুম-লিংডিংই যে নীলপাহাড়ি, আর ওই বাড়িটাই যে ঝাউবাংলো সে বিষয়ে তখন সন্দেহ নেই। এখন মনে হয়, থাকলেই ভালো হত। আরো ঘুরে বেড়ানো যেত তাহলে, আরো খোঁজা যেত। জীবনের কিছুই তো আর গল্পের মতো হয় না। এক গল্পের ওপর অন্য গল্পের আস্তরণ পড়ে, গল্পের নীলপাহাড়ি ঝাউবাংলো সব বাস্তবের হেরিটেজে আর হিংস্র লোভী রাজনীতির নোংরায় ঢেকে যায়। সে নোংরা সরানোর ক্ষমতা কজনের থাকে? তার চেয়ে বরং মেনে নিই, আপোস করি। যেমন আমি তাকদায় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। ওর ডানদিক বাঁদিক দিয়ে ঘুরি, অন্য গ্রামেগঞ্জে যাই। তাকদায় যাই না। কদাচ না।
Powered by Froala Editor