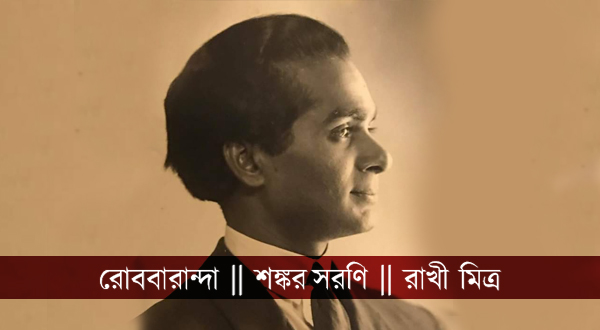সময়ভ্রমণ – ২২
আগের পর্বে
উপনিবেশগুলিতে নিসর্গ তৈরি বা ল্যাণ্ডস্কেপিং-এর ভাবনা আমদানি করেছিলেন সাহেবরাই। তড়াইয়ের জঙ্গলের প্রাকৃতিক চেহারাকে নষ্ট করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন ছবির মতো করে। সেই পদ্ধতির উপরেই দাঁড়িয়ে আজকের পর্যটন শিল্প। জঙ্গল কেটে চৌকো চৌকো খোপে বসল চা বাগান, সাহেবদের বসতি, কুলিকামিনদের থাকার জায়গা। তার মধ্যেই কিছুটা জায়গায় সাজানো জঙ্গল। যদিও শিলিগুড়ি শহরে এক পুরনো স্টেশন ছাড়া সাহেবদের কোনো ছাপ সেভাবে পড়েনি। আর তাই সেখানকার ঐতিহ্যকেও স্বীকার করেননি কেউ। নব্বইয়ের দশক থেকে শহর বড় হতে শুরু করল। উন্নয়ন শুরু হল। কিন্তু বড় হওয়া মানেই কি কুৎসিত হয়ে ওঠা। তড়াইয়ের অন্যান্য অঞ্চলের মতো রং হারাতে শুরু করল শিলিগুড়িও।
শিলিগুড়ি শহর থেকে বেরিয়ে, দার্জিলিং মোড় ছাড়িয়ে, বড় রাস্তা ধরে বাগডোগরার দিকে যাচ্ছি। একটু যেতেই জমি উঁচু হতে থাকে, টিলা টিলা মতো, কিন্তু টিলা নয়, ডাঙা জমি। তরাই জুড়ে এরকম উঁচু ডাঙা প্রায় সর্বত্র। সায়েবশাসন শুরু হবার আগে অবধি এই জমিগুলোতে বড় বড় শালগাছের ঘন জঙ্গল থাকত। যে জায়গাটা এখন মরাহাজা চাঁদমণি বাগানের ভূত, এবং শহরের মলমন্ডিত য়্যাপার্টমেন্ট-চর্চিত বর্তমান ভবিষ্যৎ, সেখানে রাস্তার দুদিকেই উঁচু ডাঙা। ডানদিকে গেলে বাগানের বড় টুকরোটা, চা গাছের ঝোপের ওপর অসংখ্য শিরিষ গাছের ছায়া, রোদ এসে পড়লে নিচে নকশিকাঁথা আলোছায়ার বুনোট। অনেক রাধাচূড়া গাছও ছিল, বসন্তে বাগানের সবুজ আর শিরিষের ঘন ছায়ায় মিশত সে সব গাছের গোলাপি-সাদা ফুলের উজ্জ্বল। বাঁদিকে, বাগানে ঢোকার পথ, কারখানা, কুলিলাইন এইসব। কারখানার পিছন দিকে শিলিগুড়ি থেকে মাটিগাড়া যাবার পুরনো পথ, ওল্ড মাটিগাড়া রোড। ডাঙা জমি চিরে যে মহাসড়ক এখন দিগন্তে উধাও হয়ে যায়, সেটা তৈরি হয়েছে পরে, সায়েবরা এ দেশ ছাড়ার পর। পুরনো সরুমতো রাস্তাটা দিয়ে মাটিগাড়া যেতে হলে চাঁদমণি বাগানের ডাঙাটা আগে পড়ত। দূর থেকে দেখা যেত, উঁচু জমির উপর বেশ কয়েকটা লম্বা, প্রাচীন শালগাছ, তার আড়ালে কারখানা। বাগান উচ্ছেদের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা যখন লড়াই শুরু করলেন, তাঁদের সভা হত কারখানার আশেপাশে। সেই সময়, তার আগেও বহুবার ওল্ড মাটিগাড়া রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শালগাছগুলো চোখে পড়েছে। ডাঙা জমিতে এরকম শালকুঞ্জ কিম্বা টুকরো বন দেখা যেত যেখানে সেখানে, এখনো কোথাও কোথাও যায়। এইসব গাছ আর বন সরকারি বনের অংশ ছিল না, বন্দোবস্ত করা জোতের আর ইজারা দেওয়া চা বাগানের জমির সঙ্গে এগুলো ফাউ হিসেবে পাওয়া যেত। বাগানের জমিতে খানিক বন রাখার চল ছিল, সেখান থেকে কুলিদের জ্বালানীর কাঠ আসত। জোতের গাছ দিয়ে কী হবে তা নির্ভর করত জোতের মালিকের ওপর। কেটে বিক্রি করা যায়, রেখেও দেওয়া যায় আবার। আমার ঘোরাঘুরি যবে থেকে শুরু, চারদিকের বাড়িঘর ক্ষেত চা বাগানের মধ্যে আচমকা এরকম বড়ো বড়ো গাছের জটলা চোখে পড়লে ভালো তো লাগতই, খানিক রোমাঞ্চমিশ্রিত উত্তেজনাও হত। প্রাচীন সব মহীরুহের সোজা উঠে যাওয়া কান্ডের গায়ে কুঁচকোনো বাদামি বাকল, তাতে ফাট ধরেছে, আর গোল গোল বয়সের দাগ। তার ওপর দিয়ে অসংখ্য পিঁপড়ে আর অন্য পোকার দলের ঘোরাফেরা, একটু উঁচুতে কাঠঠোকরার গর্ত। গুঁড়ি থেকে যেখানে ডালপালা বেরিয়ে, সবুজ-লাল-হলদে পাতার ভার নিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে ওপরে নিচের আকাশে, সেখানে, তার কিছু নিচে বা ওপরে নানারকমের ফার্ন আর অর্কিড, তার কোনটা থেকে সাদা ফুলের ছড়া বেরিয়ে হাওয়ায় দুলছে, কোনটা থেকে লাল বা গোলাপি। গাছের চুড়োয়, মেঘের ঠিক নিচে পাখিদের বাস। কোনো কোনো জমিতে শাল গাছের দীর্ঘ ছায়ায় অন্য অনেক গাছ জন্মাত। শাল গাছ কাটা হয়ে, কাঠ হয়ে চালান হয়ে যাবার পরেও সেই সব গাছ বেঁচে থাকত অনেকদিন।
চাঁদমণির গাছগুলো এখনো আছে কি? অনেকদিন পর ওই পথে গিয়েছিলাম, চোখে পড়ল না। কে খোঁজ রাখে, কেনই বা? মাটিগাড়া থেকে খাপরাইলের দিকে যেতে ডানহাতে বাঁহাতে বেশ কিছু পুরনো গাছ থেকে গিয়েছিলো, সেগুলোর প্রায় কিছুই নেই। বছর কুড়ি-পঁচিশ আগেও, ওই পথ ধরে কিছুদূর গেলেই এখানে ওখানে বড় গাছ দেখা যেত। শাল তো ছিলোই, সেই সঙ্গে শিশু, শিমূল। বাঁদিকে জমি নিচু হয়ে বালাসন নদীতে নামত। নদীর পাড়ে অনেকটা ঘাসে ঢাকা জমি, সে জমিতে উত্তরবঙ্গের প্রথম দুগ্ধ সমবায়, হিমূলের ঝলমলে নতুন অফিস, কারখানা এসব তৈরি হয়েছিল। পাহাড় আর তরাই ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে দুধ আসতো হিমূলে, সেখান থেকে শহরে যেত। কিছুটা পিছনে, মাটিগাড়ায়, কাঞ্চন নামের আরেকটা সমবায়-কারখানা হয়েছিলো, সেখানে তৈরি হত কমলালেবু আর আনারসের নানারকম সুস্বাদু জ্যামজেলি মারমালেড।
সত্তরের শেষাশেষি যখন হিমূল আর কাঞ্চন প্রথম চালু হয়, তরাইয়ের বাসিন্দারা খুব উত্তেজিত হয়েছিলেন। ঝোড়ো সত্তরের রীতি অনুযায়ী, আমাদের পাড়ার দাদারা স্কুল পুড়িয়ে, বোমা বেঁধে, লাল কালিতে লেখা বিপ্লবী পোস্টার মেরে হুলুস্থুল করছিলেন, তাঁদের অনেকেই গোৎ খেয়ে কল্যাণী বা হরিণঘাটা এমন কোথাও দুগ্ধ-প্ৰযুক্তি বা ডেয়ারি টেকনোলজি পড়তে চলে গেলেন, ফিরে এসে হিমূলে চাকরি করতে ঢুকলেন। তাঁদের কাছ থেকে এবং অন্যভাবেও হিমুল সম্পর্কে নানা খবর পাওয়া যেত। শিলিগুড়ির পাড়ায় পাড়ায় হিমূলের প্যাকেট দুধ আসা শুরু হল, সেই সঙ্গে মাখন, আইসক্রিম, এই সব। হিমূল কারখানার ভিতরে, বালাসনের পাড়ে, বাঁশ-খড় দিয়ে সুদৃশ্য মিল্ক বার বানানো হয়েছিল। ভিতর-পাহাড়ের বস্তিগুলোয় আর পাহাড়-ডুয়ার্সের টঙিয়া গ্রামে প্রধানত মেয়েদের নিয়ে ছোট ছোট সমবায় গড়ে উঠল, দুধ ঠান্ডা রাখার জন্য হিমূল থেকে অনেকগুলো চিলিং প্ল্যান্ট বসানো হল। হিমূলের দুধের গাড়ি পাহাড়-জঙ্গলের ভিতরে চলে গিয়ে কারখানা অবধি দুধ নিয়ে আসতো। কাঞ্চনের গল্পটাও একরকম। তরাই-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আনারসের চাষ হতো। পাহাড়ে ফলতো কমলালেবু। ফল জমিয়ে রাখা যায় না, সবটা চালান দেওয়াও যায় না, ফলন যা হতো তার অনেকটাই নষ্ট হতো। ফল নিয়ে শিল্পচেষ্টার কথা সরকারি মহলে দীর্ঘকাল চলেছিল, কাজের কাজ হয়নি। দার্জিলিং-জলপাইগুড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে জ্যামজেলি বানানো শেখানো হত, এই পর্যন্ত। কাঞ্চন তৈরি হবার পর মনে হয়েছিল, দীর্ঘদিনের প্রয়োজন মিটতে চলেছে। ফলচাষীদের নিয়ে ছোট ছোট সমবায় তৈরি করা হলো, তাঁদের বাগানের ফল কাঞ্চনের কারখানায় আসত, কাঞ্চনের পরিচালক-সমিতির মধ্যেও সমবায়ের প্রতিনিধিরা ছিলেন।
এই অঞ্চলে হিমূল-কাঞ্চনের মতো কিছু আগে তো ছিলোই না, এখনও নেই। ফলে লোকের উত্তেজনার কারণ ছিল। তাছাড়া, হিমূল কাঞ্চন দুটোই শুরু হচ্ছে বাংলায় বাম সরকার আসার ঠিক পরপরই, গ্রামে শহরে দিন বদলের হাওয়া। মনে হচ্ছিল একটা অন্য সময় শুরু হচ্ছে, এমন এক উন্নয়নের সময়, যেখানে সাদাকালো সায়েবরা নন, সাধারণত হিসেবের বাইরে থাকা আম মানুষেরা সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারবেন।
আরও পড়ুন
তরাই: নিসর্গ নির্মাণ, ছবি তৈরি ও ছবি ভাঙা
হায়, কিছুই থাকে না, কেন যে থাকে না। না থাকার নষ্ট বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার যে বিলাপ আমাদের পাহাড়-সমতলের প্রতি ধূলিকণা পাথর থেকে ছিটকে উঠতে থাকে সর্বক্ষণ, হিমূল কাঞ্চন সেই সর্বব্যপী বিষাদসঙ্গীতের অংশ হয়ে গেল। দুটো সংস্থাই এখন বিলুপ্ত। শালবন, ডাঙা জমি, ফাঁকা মাঠ ও চা বাগানের মতো, সমবায় ও কারখানাও বিলুপ্ত হয়ে থাকে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হিমূল প্রথমে রুগ্ন হল। দুধের যোগানে ভাঁটা পড়ছিল। পাহাড়ের গ্রাম থেকে, ডুয়ার্সের কোন কোন টঙিয়া থেকে দুধ সরবরাহ হত, অন্য গ্রামের লোক মুখ ঘুরিয়ে থাকতেন। হিমূলের কর্মীরা দুধের গুণমান মাপার যন্ত্র ল্যাকটোমিটার দিয়ে দুধ পরীক্ষা করতেন, সেই অনুযায়ী দাম ঠিক হত। সমতলের দুধ-ব্যবসায়ীরা একে তো গ্রামে গ্রামে দাদন দিয়ে রাখত, জল মেশানো পাতলা দুধ কিনতেও তাদের আপত্তি ছিল না। ফলে, হিমূলে দুধ বেচা বা সমবায় তৈরির বিষয়ে বহু লোকের অনীহা ছিলো। ওদিকে শহরে দুধের যোগান ঠিক রাখতে হবে, কারখানাও চালাতে হবে, হিমূল কর্তারা বাইরে থেকে মিল্ক পাউডার কিনে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। এসব আশির শেষদিক আর নব্বইয়ের গোড়ার কথা। এর পর থেকে কী করে কী করে কীসব হতে থাকল, শোনা গেল, হিমূলের বোর্ডে থাকা সরকারি লোকজন আর বড় অফিসাররা মিলেজুলে সংস্থাটিকে লাটে তুলছেন। হিমূলের কর্মীদের বক্তব্য ছিল, পুকুরচুরি চলছে। ওদিকে কাঞ্চনেও সেই এক গল্প। সরকার-নিযুক্ত অফিসারেরা আ-গলা-বুক দুর্নীতিদহে নিমগ্ন, মাল তৈরি হয় কিন্তু বিক্রি হয় না, সমবায়গুলো ফলের দাম পায় না। হিমূল আর কাঞ্চন, দু জায়গাতেই সরকারি তদন্ত ইত্যাদি হলো। শেষমেশ দুটো সংস্থাই উঠে গেল।
উন্নয়ন বড় মায়াময়। হিমূল আর কাঞ্চন যখন ধুঁকছে ও বন্ধ হচ্ছে, চাঁদমণি বাগান উঠিয়ে নগরায়ণ চলছে, তরাই-এর পুরোনো জোত এলাকাগুলোয় চাষ বন্ধ করে ছোট চা বাগান তৈরি হচ্ছে। সে গল্প অন্য সময় করা যাবে। আমরা বলছিলাম নিসর্গের কথা। সায়েবি নিসর্গ, পুঁজির নিসর্গ। সায়েবরা চলে যাবার পরের নিসর্গও তাই। একটা ছবির মতো, অন্যটা নয়। অথবা ছবি বলতে আগে যা বোঝা হত, এখন হয় না। পুরোনো ছবির মধ্যে নতুন ছবি ঢুকে আসছে কখনোসখনো জোর করেই। তরাইয়ের নিসর্গ এত দ্রুত বদলাচ্ছে যে হিসেব রাখা যায় না। একটা জায়গা বহুদিন ধরে একরকম, যেতেও হয় না, চোখ কী দেখবে মন আগে থেকেই জানে। ওপর-বাগডোগরা থেকে পানিঘাটার পথ যাচ্ছে ব্যাঙডুবি হয়ে। ব্যাঙডুবির বিশাল সেনাছাউনি ঢোকার মুখে বাঁ হাতে ঢেউ-খেলানো গাঢ় সবুজ মাঠ, মাঠ শেষ হলে শালবন। মাঠের পাশ দিয়ে রাস্তা বন পর্যন্ত পৌঁছোয়। সে মাঠও সেনাবাহিনীর সম্পত্তি, সেনাসায়েবরা সেখানে গলফ খেলেন। তা খেলুন। মাঠটা দেখতে বড় ভালো ছিলো। হঠাৎ একদিন গিয়ে দেখি, মাঠ আছে, অথচ আর দেখা যাচ্ছে না, মাঠ ঘিরে উঁচু, পুরু, তারের বেড়া পড়েছে। পরে দেখলাম, শুধু সে মাঠ কেন, মাটিগাড়া থেকে খাপরাইল হয়ে গাড়িধুরার পথে বা শুকনা থেকে অদলপুরের পথে যত ফাঁকা মাঠ ছিল, সবগুলোই পাকানো পাকানো কাঁটাতারের সাতপুরু বেড়া দিয়ে ঘেরা। ওই মাঠগুলোয় আর ব্যাঙডুবি-খাপরাইল-শুকনার বিস্তীর্ণ সেনাছাউনির সর্বত্র বড় বড় পুরোনো গাছ ছিলো, শাল বেশি, অন্য গাছও। শিমূলবাড়ি চা বাগান থেকে ডানহাতে রোহিনীর পথে যেতে বসন্তে দুপাশের মাঠ লাল হয়ে থাকত মাদারফুলের রঙে। সেদিন অবধিও ছিলো, এখন নেই। সেনাবাহিনীর নতুন ব্যারাক ইত্যাদি হয়েছে, নতুন বেড়াও। অন্য জায়গাতেও গাছ কমছে, বাড়ি বাড়ছে। আইনে বলা আছে, সেনাছাউনির মধ্যের গাছ কাটতে গেলেও বনদপ্তরের অনুমতি লাগে। গাছ কাটা নিয়ে সেনাসায়েবদের সঙ্গে বনসায়েবদের ঝগড়াবিবাদ এমনকি মামলা হচ্ছে, একাধিকবার দেখেছি। এখন বোধহয় মিলমিশ হয়ে গেছে।
আরও পড়ুন
বদলে যাওয়া তরাই বা শিলিগুড়ি-চরিত (২)
শুধু সেনাছাউনি কেন? শুকনা দিয়ে ঢোকা যাক কিম্বা খাপরাইল হয়ে, পাহাড়ের গোড়ায় গাড়িধুরা পৌঁছোনোর পথটি বড় মনোরম। সেনাএলাকা শেষ হয়ে গেলে বালিপাথরে বোঝাই রক্তি নদী, সেখান থেকে জমি উঁচু হতে শুরু করল, ডানদিকে বামনপোখরির বিখ্যাত সেগুনজঙ্গল, বাঁদিকে বালাসন। গাড়িধুরা আসার আগেই জমি নিচে নামছে, নিচে ছড়িয়ে আছে একেবারে ছবির মতো নিঃশব্দ, শান্ত নির্জন উপত্যকা। ডানপাশের পাহাড় থেকে সেগুনবন গড়িয়ে এসে একফালি চা বাগানে মিশছে, বাঁদিকের মাঠে ইতস্তত দু একটি গাছ, ঝোপঝাড়, তার মাঝখান দিয়ে স্বচ্ছ জলের এক নদী বয়ে যাচ্ছে। গাড়িধুরা বাজার বলতে হাতে গোনা গুটি কয়েক বাড়ি, দোকান। সোজা রাস্তা চলে যাচ্ছে পাঙ্খাবাড়ি হয়ে খরসঙ, বাঁহাতের পথ মরিয়ানবাড়ি বাগান, দুধে বাজার হয়ে বালাসনের পুল পেরিয়ে মিরিক। গাড়িধুরা বাজার থেকে ডানহাতি একটা বনপথ যাচ্ছে বামনপোখরির এক-ঘরের পুরোনো বনবাংলো হয়ে বামনপোখরি টঙিয়ায়। গ্রামে না ঢুকে গাড়িধুরার নদীটা ধরে এগুলে আশ্চর্য সুন্দর একটা জায়গায় পৌঁছোনো যেত। দুদিকের উঁচু ডাঙা জমির মধ্য দিয়ে নদীর সঙ্কীর্ণ গিরিখাত, সেখানে বড় বড় পাথর। দুটো পাথরের মধ্যে জল জমে তৈরি হয়েছে টলটলে জলের প্রাকৃতিক কুণ্ড, তার নিচ অবধি দেখা যায়। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে স্নান করা যেতো সে কুন্ডে। বসন্তে আর গ্রীষ্মে যখন অন্য সব পাহাড়ি নদীর জল পাথরবালির নিচে লুকিয়ে পড়ে, এ নদীতে তখনো জল থাকে। অনেকদিন ওইদিকে যাওয়া হয় না, এখনো থাকে কিনা বলা মুশকিল। গাড়িধুরার নির্জন উপত্যকা জুড়ে ঘরবাড়ি দোকান উঠছে তো উঠছেই। পুরোটাই বনভূমি, সেখানে এভাবে ঘরবাড়ি বানানো যায় না। যায় না কে বলল? নদীটাকে আলাদা করে বোঝা যায় না, আবর্জনায় ভর্তি, শহরের, বাজারের নদী যেমন হয়।
অনেক নদীর কথা, মাঠের কথা, বনের কথা মনে হয়। কিছু আছে, বেশির ভাগই নেই, বা না থাকার মতন। যা আছে তার দু একটির কথা আগে বলি। বামনপোখরির সেগুনজঙ্গল সায়েবি বনশাসনের একেবারে গোড়ার দিকে লাগানো। শালবনের এলাকায় বার্মাদেশীয় সেগুন গাছ টিঁকবে কিনা তা নিয়ে বনসায়েবদের সন্দেহ ছিলো। স্লিকের যে প্রতিবেদনের কথা আগে এসেছে সেখানে বামনপোখরির টিকজঙ্গলের কথা বিস্তারিত বলা আছে। ছোট এক টুকরো প্ল্যান্টেশান বাড়তে বাড়তে পাহাড় বেয়ে উঠতে থাকে, কাটা পড়ে, আবার নতুন গাছ লাগানো হয়। পুরো অঞ্চলে অন্য গাছ বলতে নেই। কী আশ্চর্য, ওই বনের ধার দিয়ে হেঁটে গেলে রক্তি নদীর গভীর গিরিখাত নজরে আসে। অদ্ভুত বন্য সে এলাকা, উঁচু উঁচু পাহাড় উঠে গেছে, বহু নিচে নদী। এদিকের সেগুন বনে খাবার যোগ্য ছোট গাছগাছালি ঘাস থাকে না বলে বুনোরাও থাকে না। অথচ বামনপোখরির বনে ডাকিয়ে হরিণ আর বনশুয়োর স্বচক্ষে দেখেছি, শুনেছি চিতাবাঘও আছে। বামনপোখরি পাহাড়ের মাথায় দুটি প্রাকৃতিক জলাশয় আছে, সেই থেকে পোখরি। বামন সম্ভবত বাউন, ব্রাহ্মণ। ওই পুকুরে কি কোন ব্রাহ্মণ পুজো দিয়েছিলেন? কে জানে!
আরও পড়ুন
বদলে যাওয়া তরাই বা শিলিগুড়ি-চরিত
বাগডোগরা-পানিঘাটা পথে, ব্যাঙডুবি বনের মধ্যে আর একটি ছোট সদানীরা জলধারা আছে। ফাইভ এফওডি-র দুর্ভেদ্য আদিম বন(অস্ত্রাগার বলে বন কাটা হয় না) থেকে বেরিয়ে সেই নদী এঁকেবেঁকে বাগডোগরা-নকসালবাড়ি রাস্তায় সন্ন্যাসীথান বাগানের গা দিয়ে বন ছেড়ে বেরুচ্ছে। নদীর ধার দিয়ে পুরোনো এক বনপথ ব্যাঙডুবি সেনাছাউনি থেকে নকসালবাড়ি রাস্তায় পড়ছে। সে পথের মাঝামাঝি বনের একেবারে ভিতরে নদীটাকে আবার পাওয়া যায়। ওই পথ ধরে সেন্ট্রাল টঙিয়া বস্তিতে পৌঁছোতে হত। যতবার যেতাম, নদীর ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতাম। বড় বড় শালগাছ, তার ছায়া পড়ত নদীর কালচে জলে। বনঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে মিশে যেত পাথরে জল ভাঙার মৃদু আওয়াজ। জায়গাটায় পিকনিকওয়ালাদের যাতায়াত শুরু হয়ে গেল, আর যাওয়া হয় না।
দুধে বাজার থেকে বালাসন পেরিয়ে চড়াই শুরু হবার ঠিক মুখটায়, বাঁ হাতে একটি সরু ভাঙাচোরা রাস্তা চলে যাচ্ছে গয়াবাড়ি চা বাগানের ডিভিসানে। সে পথে মুক্তিখোলা নদীর উচ্ছল ধারা। বর্ষায় সে জায়গা অপরূপ। মেঘ নেমে আসে পাহাড় বেয়ে নদী অবধি, নদী উপছে পড়ে জলে। সেখানেও ইদানিং আমোদসন্ধানীদের ভিড় বাড়ছে, বড়ো একটা যাই না।
আরও পড়ুন
তরাই-মোরাং-এ সায়েবসময়
আরো একটা নদী, নদীকে ঘিরে শালবন, এখনো অবধি আছে। বাগডোগরা থেকে কলকাতা ও বিহারগামী বড় সড়কে একসময়ের নামকরা সায়েবি বাগান গঙ্গারাম। সেই বাগানে ঢুকতেই উঁচু ডাঙাজমিতে পথ কেটে বয়ে গেছে শীর্ণ জলস্রোত। দুপাড়ে শালগাছ, কিছু জারুল। গঙ্গারাম বাগানের দুর্দশা চলছিলো শুনেছি। বাগান খারাপ হয়ে গেলে সেখানকার গাছটাছও সচরাচর থাকে না, হয় মালিক নয় শ্রমিকেরাই তা কেটে বিক্রি করে দেয়। গঙ্গারামের গাছগুলো কি করে থেকে গেল, ভাবলে আশ্চর্য লাগে।
বাগডোগরা থেকে নকশালবাড়ির পথে পাহাড়গুমিয়া বাগান, তার পিছনে বিজয়নগর বাগান। তার পাশ দিয়ে পথ গিয়েছে বুড়াগঞ্জের দিকে। বুড়াগঞ্জ নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র, সেকারণে বিখ্যাত। সে গল্পে ঢুকছি না। বিজয়নগর বাগান থেকে বুড়াগঞ্জ যেতে অনেকটা জায়গা জুড়ে উঁচু ডাঙা জমি। তিরিশ বছর আগে প্রথম সে পথে যাচ্ছি, চারদিক নিস্তব্ধ, কোথাও জনমনিষ্যি নেই, ডাঙা জমি জুড়ে ছড়ানো কিছু বন্য লতাগুল্ম, এখানে ওখানে কাটা গুঁড়ি। একটাও বড় গাছ নেই। মানে বন নয়, বনের ভূত। পরে শুনেছিলাম, ওখানে একটা আস্ত শালবন ছিল। বনদপ্তরের দলিল দেখে জানা গিয়েছিল, জায়গাটার নাম উত্তমচাঁদের ছাট। জোত জঙ্গল। হাতি এসে আশ্রয় নিত বলে বুড়াগঞ্জের লোকেরা এক রাতে বন কেটে সাফ করে দিয়েছিল। বুড়াগঞ্জের কৃষক আন্দোলনের তরুণ নেতা এই গল্পটা করেছিলেন। আন্দোলন তখন বহুবিভক্ত, ওঁদের টুকরোর প্রধান ছিলেন নকশালবাড়ির লড়াইয়ের প্রবাদপ্রতিম এক নেতা। তিনি এখন নেই। নকশালবাড়ি আন্দোলনের মূল চরিত্রদের প্রায় সবাই চলে গেছেন একে একে। আরো যা যা গেছে, নেই, সে সব কথা ধীরেসুস্থে বলা যাবে।
Powered by Froala Editor