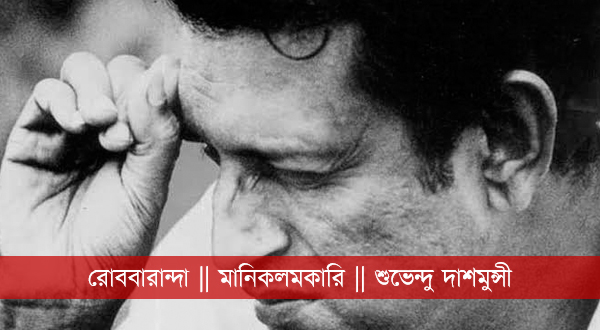সময়ভ্রমণ – ১৫
আগের পর্বে
১৮৬৫-তে ভারতীয় বন দপ্তর পত্তন হবার পর নতুন আইন। শুকনা-সেবকের বনের দখল চলে যায় সায়েবদের হাতে। সরকারি বন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় লেপচা, মেচিয়াদের। শিলিগুড়ির একটু বাইরে গেলেই সেভকের বন শুরু হয়ে যায়। সাহেবরা সেখানে মাটিতে গর্ত করে রেখে দিত নুন। তারপর নুন চাটতে এলে গুলি করে শিকার করা হত হরিণ, বন্যশুয়োর কিংবা চিতাদের। তবে আদি নেটিভদের তাড়িয়ে দেওয়ার যুক্তি কী ছিল? কালিঝোরা ছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রিয় জায়গা। থেকেওছেন বহুবার। এখন সেই জায়গা জুড়ে জন্ম নিয়েছে বহু মন্দির। সাহেবদের আধিপত্য বিস্তারের আগে সেভকের শুকনো বনে ছিল প্রাকৃতিক রাবার গাছও। তাও অবলুপ্ত আজ। লাটপাঞ্চারের জঙ্গলের ভিতর রয়েছে বহু গুহা। তবে কী আছে আর কী নেই তার মধ্যে, তা আজও রহস্য।
মাহালদি নদী ও চিপলেখোলার সঙ্গমস্থল থেকে নদী বরাবর হাঁটতে থাকলে উঁচু নিচু পাথর পেরিয়ে গোলাঘাট পৌঁছোনো যায়। গভীর বনের মধ্যে বয়ে চলা নদী, দুপাশে জংগলাকীর্ণ পাহাড়, সে জায়গার নাম গোলাঘাট কেন সন্ধান পাওয়া যায়না। নামটা অবশ্য পরে শোনা। আমরা জায়গাটাকে চিনতাম শুকনা লেক বলে। সম্ভবত ১৯৭২-৭৩ নাগাদ মহানদীর ওপর বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়। শিলিগুড়ি থেকে শুকনা বাজার ও বাজার লাগোয়া নিঃঝুম ছোট স্টেশন ছাড়িয়ে হিলকার্ট রোড ধরে পাহাড়ের দিকে একটু যেতেই ডান হাতি বনপথ চলে যায় মহানন্দা অভয়ারণ্যের ভিতরে। পাহাড় শুরু হবার আগেই জমি উঁচু হতে শুরু করে, ডাঙা জমির উপর শালের পুরোনো বাগান অর্থাৎ প্ল্যান্টেশান। সেখানে সায়েবি আমলের একটা বাংলো এখনো টিঁকে আছে, অবশ্য অক্ষত কলেবরে নয়, ফেরবদল হয়েছে। বাংলোয় আমলা মন্ত্রী ইত্যাদির যাতায়াত লেগে থাকত, এখনো থাকে। শুনতে পাই, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সেখানে এসে থেকেছেন এবং হেঁটে হেঁটে আশপাশের বনগ্রামে গিয়েছেন। বনবস্তিগুলোকে ইদানিং সরকারিভাবে বনছায়া বলে ডাকা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর আদেশে। সবুজ সুন্দর বনের মধ্যে বস্তি কেন, ছায়া থাকবে, এমন কিছু একটা তাঁর মনে হয়েছিল। শুকনা বাংলোয় আগের মুখ্যমন্ত্রীরাও থেকেছেন, মিটিং করেছেন, জ্যোতি বসু, তারও আগে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।
ভিআইপি আনাগোনার কারণেই হোক বা উন্নয়নবাসনায় তাড়িত হয়ে, সরকারি বনদপ্তর গোলাঘাটে শুকনা লেক তৈরি করে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে শুকনা থেকে হাঁটতে হাঁটতে এক শীতের দুপুরে সেখানে পৌঁছোই। সেই পুরাকালেও হইহই পিকনিকবাজদের ভিড় ছিল, তৎসহ বহুমাইক-উৎসারিত সুরেলা গাঁকগাঁক, হাম তুমি এক কামরে মে বন্ধ হো। সবে ববি ফিল্ম রিলিজ করেছে কি করেনি, হাটে মাঠে ঘাটে(এবং বনে) গান অহোরাত্র বাজছে।
শুকনা বন আপিস থেকে বনপথ ধরে আট কিলোমিটার হাঁটতে হত লেক অবধি, তার মধ্যেই পাহাড় চলে আসতো বাঁদিকে। যে কেউ যখন তখন ঢুকে পড়তে পারত, বাধা ছিল না। পরে গেট ইত্যাদি হয়, পাহারা বসে, টিকিট কেটে ঢুকবার ব্যবস্থা হয়। তা হোক। শুকনা থেকে গোলাঘাট আট কিলোমিটার পথের পুরোটাই শাল ও সেগুন প্ল্যান্টেশানের মধ্য দিয়ে, তবে বনে ঢুকে পড়লে খারাপ লাগত না। পরে, নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সেগুনবাগান কেটে খালি জায়গায় ঘাস লাগিয়ে সল্ট লিক বানিয়ে সবুজ রং করা কাঠের নজরমিনার অর্থাৎ ওয়াচটাওয়ার বসিয়ে 'গ্লেড' তৈরির চেষ্টা হয়। অভয়ারণ্য হলে কি হয়, শুকনা-সেভকের বনে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা তখন ক্রমহ্রাসমান, সকালসন্ধ্যা বন চষে ফেললেও 'সাইটিং' হয় না, মানে কিছু দেখা যায় না। বনে বন্যেরা সুন্দর বোধে বনদপ্তর বাইরের মৃগদাব থেকে হিঁচড়ে টেনে আনা চিতল হরিণ বনে ছাড়তে শুরু করেছে। হরিণদের ঘুম পাড়ানি গুলি ছুঁড়ে জাল দিয়ে পাকড়াও করা হত, দৌড়োদৌড়িতে, শকে, অনেক হরিণ হার্টফেল করে মারা যেত। কিছু করার নেই। হরিণ না থাকলে বাঘ কী খাবে, লোকেই বা কী দেখবে। বেশ কয়েক দফায় হরিণ ছাড়া হয়, মনে আছে। সে হরিণদের সন্তান সন্ততিদের কেউ কেউ অদ্যাবধি বেঁচে থাকতেও পারে। বাঘের পেটে না যাক, লোকের পেটে যে তাদের গরিষ্ঠাংশ গেছে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শুকনা, শালবাড়ি, এদিকে শালুগাড়া চম্পাসারি এমনকি শহরের মধ্যে হায়দারপাড়া বাজারেও হরিণমাংস বিক্রি হতো, শুনেছি। সবাই পেত না। যারা সন্ধান জানত তারা। আগে বলে রাখতে হত। গোলাঘাট-শুকনা লেকের পথের পাশের গ্লেডে চিতল হরিণের দল এক আধ বার চোখে পড়েছে, সেও নব্বইয়ের শেষের দিকে।
ওই পথে যেতে যেতে চোখে পড়তো রংচঙে ঝোলা ল্যাজ বনমোরগ আর ধূসর বনমুরগি, ঝলমলে ময়ূর আর বেরঙ ময়ূরী, বড়জোর এক-আধটা বনশুয়োর, অনেক বাঁদর। আর, হাতি না হোক, পথ জুড়ে হাতির শুকনো, আধ-শুকনো এবং কখনো-সখনো ধোঁয়া ওঠা টাটকা নাদি। পিকনিকের সময় লেকের কাছাকাছি এলাকায় কিছু চেঁচামেচি(মাইক বাজানো এবং পিকনিক পরে বন্ধ করা হয়) হইচই, বাকি সময়টা বনের শব্দ। পাখির ডাক, বাঁদরের কিচকিচ, বিকেলের দিকে ময়ূরের কর্কশ ক্যা-ও-ও-ও, দূরাগত ডাকিয়ে হরিণ বা কাঁক্কর হরিণের ডাক, আরো দূরে হাতির ডাল ভাঙার শব্দ, সব ছাপিয়ে বনঝিঁঝিঁর তীক্ষ্ণ তীব্র কলতান। পিকনিককাল ছাড়া অন্য সময়ে শুকনা লেক ঝিমঘুমন্ত, নির্জন। সম্ভবত তিরানব্বই-এর বন্যায় মহানদীর ওপরের বাঁধটা ভেঙেচুরে যায়, নদী দিক বদলে অন্যদিকে যেতে শুরু করে। শুকনা লেকেরও অপমৃত্যু ঘটে। বাঁধ পার হয়ে যে রাস্তা দশ মাইলের দিকে যেত, সেটার বেশ খানিকটা নদীতে চলে যায়। পাহাড়ের উপর উপর সরু একটা পথ বানানো হয়েছিল, সেটাও ভেঙে গেছে বোধহয়।
নব্বইয়ের গোড়ায় লাটপাঞ্চারের বন থেকে দুটি রোমশ কালো ভাল্লুক ছানাকে উদ্ধার করে গোলাঘাটে রাখা হয়েছিলো। ছানা দুটি এ গাছ ও গাছ এবং এ চাল ও চাল করে বেড়াত, নজর রাখত কে আসছে, কী খাচ্ছে। ভাগ না দিয়ে কিছু খাওয়া যেত না, যতক্ষণ না দেওয়া হত তারা নখ দিয়ে আঁচড়াত, ঘোঁক-ঘোঁক আওয়াজও করতো। ভাল্লুকছানাদের বনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো না চিড়িয়াখানায় পাঠানো হয়েছিলো মনে নেই।
মাহালদি-মহানদী-মহানন্দার আসল বন শুরু হত গোলাঘাটের পর থেকে। গোলাঘাট থেকে দশ মাইল পর্যন্ত বারো-তেরো কিলোমিটার গাড়ির পথ। এই পথ থেকে বাঁদিকে পাহাড়মুখো সরু সরু রাস্তা ঢুকে যাচ্ছে দুর্ভেদ্য বনের গভীরে। একটা পথ যেতো চকলঙে, চকলঙ খোলায়। ভরা বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে চকলঙে জল থাকত না বললেই হয়। নদীর বালিতে, গর্তের মধ্যে জমা জলের পাশের কাদায় অসংখ্য বুনোচিহ্ন। বড় সম্বর হরিণের চ্যাপ্টা গোছের খুর, বাদামি ডাকিয়ে হরিণের ছোট, ঈষৎ গভীর খুর, বুনো শুয়োরের গোল খুর, বুনো গরু বা গউরের গোল, চ্যাপ্টা খুর, ভোঁদড় আর বেজির ছোট খাবার দাগ। সেইসঙ্গে কখনো আবছা কখনো পরিষ্কার বাঘের পাঞ্জা। বাঘ বলতে বড় বাঘ। তরাইয়ের বন বাঘের জন্য বিখ্যাত ছিল। নব্বইয়ের শেষ অবধি মহানন্দার জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় বাঘের পাঞ্জাছাপ দেখেছি, চকলঙে, গুলমায়, ঘোড়ামারায়, হিলেখোলায়। ওইসব এলাকায় উঁচুজমির শাল আর নদীচরের শিমুল-শিরিষ-খয়ের বনের সঙ্গে মিশে আছে ভেজা চিরসবুজ বন, ওয়েট এভারগ্রিন ফরেস্ট। সে বন বড় গাছ আর লতাগুল্মের সবুজ নিরেট দেয়াল, ফাঁক খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্ষার আগে পরে প্রায় প্রত্যেক ঘাসপাতায় ডোরাকাটা আর কালো জোঁক শুঁড় বাড়িয়ে কিলবিল করে, গেলেই ছেঁকে ধরে। বনের মধ্যে নদী, ঝোরা, নালা, কোনটা ছোট, কোনটা বড়। পথ চেনা না থাকলে কোথায় কোনদিকে যেতে হবে বোঝা যায় না। পরিচিত ও অনাম্নী সব জলধারা এসে পড়ছে মহানদী না হয় গুলমায়। পশ্চিমের নদীনালা গিয়ে মিশছে তিস্তায়।
আরও পড়ুন
বনপথ ধরে--মাহালদি নদী, শুকনা-সেভকের জঙ্গল
গোলাঘাট থেকে দশ মাইল পথে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ফলে শুকনা-সেভকের আসল পুরনো বন দেখবার সুযোগ নেই। বনের গভীরে বুনোদের দল বেঁচেবর্তে আছে কি না বোঝার উপায়ও নেই। বাঘ নেই একরকম নিশ্চিত। নব্বইয়ের মাঝামাঝি থেকে দুহাজার দশ, তরাই ডুয়ার্সের বন থেকে বাঘ অবলুপ্ত হয়ে গেল। কেন, কী করে, জানার উপায় নেই। বনকর্তারা বলবেন লোকে মেরে ফেলেছে, আশপাশের গ্রামের লোক, চা বাগানের আদিবাসী শ্রমিক। বিশ্বাস করা মুশকিল। বাঘ মরলে জানাজানি হয়ে যায়। উত্তরপ্রদেশের, উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন বনে, মধ্যপ্রদেশে এবং অন্যত্র বিষ দিয়ে বা অন্যভাবে বাঘ মারার ঘটনা ঘটেছে। বাঘ গরু ছাগল খেতে থাকলে, মানুষ মারলে, এরকম ঘটনা ঘটে, তাও সবসময় নয়। শুকনা-সেভক এলাকায় যে সব জনবসতি তার অধিকাংশের বয়স একশো বছরের বেশি। কিছু কিছু প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়ের, তাদের বয়সের আন্দাজ করা যায় না। এই সব গ্রামের মানুষেরা হঠাৎ বাঘ মারতে যাবেন কেন, এত মারবেন যে বন থেকে বাঘ উধাও হয়ে যাবে? তাও বছর পনেরো-কুড়ির মধ্যে? বিশ্বাস হয় না। দ্বিতীয় আর একটা ব্যাখ্যা হচ্ছে সংগঠিত, হিংস্র চোরা শিকার। তিব্বত ভুটান নেপাল বার্মা থাইল্যান্ড ভিয়েতনাম লাওস চিন হয়ে ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলোয় চোরাশিকারের চল আছে। শিকার করা প্রাণীর দেহাংশ চড়া দামে বিক্রি হয়। হাতির দাঁত, কালো ভাল্লুকের পিত্ত বা বাইল, গন্ডারের খড়্গ, বাকিদের চামড়া, শিঙ। বাঘের সবকিছু। চামড়া, মাংস, হাড়, নখ। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর দেশজ চিকিৎসায় এসব ব্যবহারের রেওয়াজ আছে। মধ্য প্রাচ্যেও ভালো বাজার।
আসাম থেকে আসা চোরাশিকারিদের দল আমাদের জঙ্গলগুলোয় ঘুরছে, এমন কথা কানে এসেছে বহুবার। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি, শিকার এবং ব্যবসা দুটোই হয়ে থাকে, সুতরাং এক্ষেত্রেও সেরকম কিছু হয়ে থাকতেই পারে, উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তা সত্বেও তৃতীয় আর একটা ব্যাখ্যা বোধহয় থেকে যায়। বাঘ এমনিতেই বংশবৃদ্ধি করে ধীরে। বনে বাঘ আর বাঘিনীর সংখ্যায় আনুপাতিক সামঞ্জস্য থাকা দরকার। বাঘের তুলনায় বাঘিনী, বা বাঘিনীর তুলনায় বাঘ কম পড়লে জিন-বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকে। পরিবারের মধ্যেই অর্ন্তমিলন বা ইন-ব্রিডিং ঘটতে থাকে, ফলে বংশগতির প্রাকৃতিক নিয়ম বিপর্যস্ত হয়। বাঘের সংখ্যা কমতে থাকে, কালক্রমে বাঘ আর থাকেই না।
বাঘ কমার একটা কারণ শিকার। চোরাশিকার নয়, উনিশ শতকের শুরু থেকে বিশ শতকের শেষ অবধি রীতিমতো আইনি শিকার চলেছে। দু একটা হাতে গোনা গেম স্যাংকচুয়ারি ছাড়া দার্জিলিং পাহাড়ের কোথাও শিকারে বাধা ছিল না। সায়েবরা তো মারতেনই, দিশি শিকারিরাও কম যেতেন না। ১৯০৯-এ ও'ম্যালির গ্যাজেটিয়ার বেরুচ্ছে, সেখানে বলা আছে জেলায় প্রচুর বাঘ, মেরে শেষ করা যায় না। বাঘ মারতে লোকে হামেশা শুকনা-সেভকের জঙ্গলে হানা দিত। শিলিগুড়ি এবং ডুয়ার্সে নামকরা সব শিকারি থাকতেন। মরা বাঘ দেখতে পাড়ার লোকে ভিড় করে আসত। আমিও দেখেছি। শিকারি দাদার ভাই শহরের বিখ্যাত খেলোয়াড়, আমাদেরও পাড়ার দাদা। তাঁর গলায়, এবং আরো অনেকের গলায় বাঘনখ ঝোলানো থাকত। ধনীদের কাঠের দোতলায় টাঙানো থাকত বাঘের চামড়া।
আরও পড়ুন
পথের কথা: ওল্ড মিলিটারি রোড
এ তো গেল সায়েবদের আর বাঙালি বড়লোকদের শিকারখেলার কথা। তরাই এলাকা ইংরেজদের দখলে আসে ১৮৫০-এ। ১৮৭৬-এ হান্টার সায়েবের, অর্থাৎ ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের লেখা বিখ্যাত বাংলার সংখ্যাতাত্বিক বিবরণের দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি খণ্ড প্রকাশিত হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে, পাহাড়-তরাই মিলিয়ে দার্জিলিং এলাকার মোট পাঁচটি টুকরো। এক, পুরোনো পাহাড়ি অঞ্চল, পাংখাবাড়ি থেকে ঘুম-জোড়বাংলো হয়ে দার্জিলিং, ১৮৩৫-এ সিকিম রাজা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থাৎ ইংরেজদের হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দেন। দুই, চেবু লামার সম্পত্তি, ঘুম থেকে সান্দাকফু-ফালুটের পাহাড়চূড়ো, যেটা সিকিম রাজা জনৈক চেবু লামাকে দিয়েছিলেন। ১৮৫০ এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাস্তিস্বরূপ এটা নিয়ে নেয়। তিন, অবশিষ্ট সিকিম পাহাড়ের অঞ্চল, এদিকে ঘুম থেকে নেপাল সীমান্ত, অন্যদিকে তিস্তা নদী অবধি। এই দুটো টুকরোও ১৮৫০-এ কোম্পানির হস্তগত হয়। চার, তিস্তার পুবদিকের ভুটান পাহাড়, আজকের কালিম্পং, ১৮৬৪-র তথাকথিত ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের পর ইংরেজ সরকারের হাতে আসে। পাঁচ, তরাই, যেটা সিকিম রাজত্বের অংশ ছিল, কিন্তু ১৮৫০-এ কোম্পানির হাতে চলে যাচ্ছে। ১৮৫০-এর পর থেকে দার্জিলিং-এ একের পর এক চা বাগানের পত্তন হতে থাকে। বাকি পাহাড় মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিবিড় বনে ঢাকা, প্রজা বসানোর বা চাষবাসের সুযোগ নেই বললেই চলে। ফলে বাকি থাকলো তরাই, ঘাসবন, জলা-জঙ্গলে ভরা। হান্টারের ভাষায়, 'অসভ্য', 'জংলি' মেচ আর ধিমলরা সেখানে থাকে। আর থাকে বুনো জানোয়ারের দল। পাহাড়ে শিকারযোগ্য প্রাণী বা গেম বিশেষ নেই, লিখছেন হান্টার। সে তুলনায় তরাই জন্তু-জানোয়ারে ভর্তি। বাঘ, গন্ডার, হাতী, বনমহিষ, হরিণ, কি নেই? এমনকি নেকড়েও ছিল দু চারটে। তরাইকে চাষযোগ্য করে প্রজা বসাতে গেলে বন পরিষ্কার করতে হবে, জানোয়ারও মারতে হবে। বুনোদের মারলে সরকারি ইনাম ছিল। ১৮৬৯-এ, জানোয়ার মারার পুরস্কার বাবদ সরকারের খরচা হচ্ছে ৩১৮ টাকা মতো, আগের পাঁচ বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি। হান্টার বলছেন ৬৯-এ, পুরস্কারমূল্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাঘ মারলে ২০ টাকা বা ২ পাউন্ড। চিতাবাঘ মারলে ১০ টাকা। হাতি মারলেও ১০। গন্ডার পিছু ৫ বা ১০ টাকা।
ইংরেজরা এ দেশ ছাড়ার পরেও খেলাচ্ছলে বাঘ শিকার চলত, সেইসঙ্গে হরিণ, বাঘের অন্যতম খাবার। শহর ছাড়ালেই বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলমাহাল, তিস্তার দুই পারে। এদিকে শুকনা-সেভকের, মহানদীর বন। পাড়ার এক শিকারি গল্প করেছিলেন, শিকারের কথা কী আর বলব। সেভক রোড ধরে একটু এগুলে, শালুগাড়া ছাড়ালে দু ধারের মাঠে সন্ধ্যা নামলেই হরিণ। গিজগিজে। আলো ফেললে জোনাকির মতো জ্বলজ্বল করত চোখ। গুলি চালালেই হল, একটা না একটার গায়ে লাগতোই। গল্পটা যিনি করেছিলেন তিনি এবং তার ভাইবোনেরা আমাদের পুরোনো পাড়ার একটা পুরোনো কাঠের বাড়িতে থাকতেন। কাঠের বাড়ি, কাঁচের জানলা, কাঠের মেঝে। নব্বইয়ের শুরুর দিকের কথা, বাড়িটা তখনই নড়বড়ে, পোড়ো। হরিণশিকারি দাদা সেতার বাজাতেন, সেতার শেখাতেন। তিনি এখন কোথায় জানি না। বাড়িটা ভাঙা পড়েছে বহুদিন।
বাঘ এবং অন্যান্য বুনোদের সংখ্যা কমার, হারিয়ে যাওয়ার একটা কারণ যদি হয় শিকার, দ্বিতীয় কারণ কাঠব্যাবসা। হান্টার হিসেব দিচ্ছেন, দার্জিলিং জেলার বনে ১৮৭০ নাগাদই দামি, কেজো কাঠ প্রায় শেষ। যা ভালো কাঠ আছে তা হয় পাঞ্চার এলাকায়, মাহালদিরামে, না হয় রংটং আর তিস্তার মধ্যবর্তী অঞ্চলে। কাঠ বাঁচাবার কারণেই প্রধানত শুকনা-তিস্তা রিজার্ভ তৈরি করা হয়। রিজার্ভের বাইরের এলাকায় তো বটেই, রিজার্ভের মধ্যেও বিস্তীর্ণ ঘাসবন বা সাভানা ছিল। ১৮৬৯-এ সরকারি বনবিভাগের প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি হচ্ছে। প্রথম প্রথম এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হত বন নিয়ে যাবতীয় সরকারি দলিলের সংকলন, প্রসিডিংস অফ লেফটেন্যান্ট গভর্নর অব বেঙ্গলের অংশ হিসেবে। কয়েক বছর পর থেকে বন বিভাগের বার্ষিক প্রগ্রেস রিপোর্ট আলাদা করে বেরোতে থাকে। ১৮৬৯-তে প্রকাশিত এচ লিডস-এর প্রতিবেদন এবং ১৮৭২-৭৩-এর প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত জে সাইকস গ্যাম্বল এস্কোয়ার-এর লেখা 'মহানদী তরাই এবং সেভক পাহাড়ি বনের সাধারণ বর্ণনা' নামের দস্তাবেজ থেকে শুকনা-সেভক বনের আদি প্রাকৃতিক চেহারা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। লিডস বলছেন পাহাড়ের বনের বেশির ভাগ গাছ কাটা হয়ে গেছে। সাইকস গ্যাম্বল বলছেন মহানদী রিজার্ভের ৮৪০৪ একরের মধ্যে ২৫৩৪ একর সাভানা, মূলত সিলিভিটা-চকলং এলাকায়।
আরও পড়ুন
সিঙ্কোনার আরো গল্প
তরাই-এর ঘাসবন সায়েব প্রশাসকেরা হিসেব কষে, পরিকল্পনামাফিক, নির্মূল করেন। শুকনা-তিস্তা রিজার্ভ বা মহানদী রিজার্ভ এলাকার মধ্যেই যে মেচ আদিবাসীরা বাস করতেন, তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। রিজার্ভের বাইরেও জুমচাষ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘাসবন আর অন্য জঙ্গল পুড়িয়ে চাষের জমি তৈরি করতেন মেচ আর ধিমলরা। হান্টারের বইতে ডক্টর ক্যাম্পবেলের ১৮৫১-য় লেখা একটি দস্তাবেজ উদ্ধৃত। মেচদের তুলো চাষ নিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ চিত্রময় বর্ণনা আছে তাতে। তুলো চাষের জন্য বালি মেশানো কালচে আঁশমাটি ব্যবহৃত হতো। একটা ফসল হয়ে গেলে জমি ফেলে রাখতে হত। শীতকালে বন পোড়ানো হত, ডালপালা ঘাসপাতা কিচ্ছু মাটি থেকে তোলা হত না। যা পড়ে থাকত সবটার ওপর বিছানো হতো ছাইয়ের আস্তরণ। বসন্তে জমি তৈরি, বর্ষার গোড়ায় বীজ রোয়া, শীতে ফসল। তুলো উঠে গেলে সে জমিতেই ধান দেওয়া হত। তারপর জমি ফেলে রাখা পুরো পাঁচ বছর। ততদিনে বন ফিরে এসেছে, আবার তুলো দেওয়া যায়। বাইরের সার নয়, সেচ নয়, অথচ এক অতিবৃষ্টি বা খরা না হলে ফসল উঠতই। কখনো কখনো তুলোবীজের সঙ্গে ছিটিয়ে দেওয়া হতো ধান। প্রথম পদ্ধতিতে চাষকে বলা হত কিল, দ্বিতীয়টাকে ঝাগরি।
তুলো থেকে সুতো কেটে কোমরে বাঁধা তাঁতে বুনে কাপড় বানাতেন মহিলারা। তার আগে গাছপালা আর মাটির রঙ দিয়ে সুতো রং করা হত। তুলোর সুতো ছাড়া মেচদের মধ্যে রেশমসুতোরও চল ছিল। এড়ি বা এন্ডি থেকে রেশমগুটি তৈরি হত।
মেচদের বাড়ি তৈরি হত ঘাস আর বাঁশ দিয়ে। ঘরগেরস্থালির সরঞ্জাম বানানোয় ব্যবহার করা হত বাঁশ, কাঠ, মাটি। বাড়ি বানানো, চাষাবাদ, শিকার, তাঁতের বা বাঁশের কাজ, এসবে ব্যক্তিমালিকানা ছিল না। যা হত সবাই মিলে। প্রতি গ্রামে নামকোআস্তে একজন গ্রা অর্থাৎ গাঁওবুড়া থাকত বটে, কিন্তু সমাজের সমস্ত কাজ যৌথ সিদ্ধান্তে হত।
আরও পড়ুন
আরো সিঙ্কোনা-কাহিনি
জুম বন্ধ করার সরকারি আদেশ মেচ সমাজজীবনকে ভেঙে তছনছ করে দিল। এ গল্পে ফেরা যাবে। এদিকে বনে আগুন না লাগলে ধান হবে না। তুলোও হবে না। তুলো না হলে সুতো নেই, পরনের পোশাক নেই। বনে ঢোকা বারণ, ফলে শিকারও বারণ। বনে আগুন না লাগলে ঘাস জন্মায় না, বাড়ে না। ঘাস না থাকলে বাড়ি তৈরি হয় কী দিয়ে?
বনে ঘোরাঘুরি সবে শুরু হয়েছে, অবাক হয়ে দেখি বনের মধ্যে লম্বা লম্বা রাস্তা কাটা, চৌখুপি মতো। শুনলাম, ওগুলো ফায়ারলাইন। আগুন লাগলেও ফাঁকা জায়গায় এসে আটকে যাবে, ছড়াতে পারবে না। আগুন আটকে দিলে ঘাসবনে বড় গাছ গজাবে দ্রুত। বেশি বৃষ্টির এলাকায় ঘাসবনে গজিয়ে উঠবে নতুন ভেজা চিরসবুজ বন, যেমন চকলঙে। চকলঙে ঘোড়ামারায় হিলেখোলায় যে বন দেখেছি, যে বনের নিবিড় ঠাসবুনোট থেকে আদিম সময়হীনতার ঘ্রাণ আসে, তা আসলে তাহলে সায়েবি বনদখলের ফল? আদিবাসীদের বনে থাকা নয়, সায়েবদের বন নিয়ন্ত্রণ? প্রকৃতিকে বদলে ফেলা, লাভের জন্য?
১৯৪৯-এ মহানদী অভয়ারণ্য বিজ্ঞাপিত। ১৯৭৬-এ মহানন্দা। নিজের চোখে দেখেছি, বনবিভাগের কাগজপত্রেও পড়েছি, অভয়ারণ্য এলাকায় কাঠ কাটাকাটি চলেছে ১৯৮৮-৮৯ অবধি। ঘাসবন, নদীচরের শিমূল-শিরিষ, ডাঙা জমির শাল, ভেজা বন, সব ফৌত, সেখানে সেগুন আর জারুলের চাষ। অভয়ারণ্য এলাকার বাইরে ঘাসবনও নেই, এমনি বন নামমাত্র। তরাই থেকে গন্ডার আর বুনো মহিষ বিলুপ্ত হয়ে যায় বিশ শতকের গোড়ায়। বাঘও অধুনা বিলুপ্ত। হাতি আর চিতাবাঘ অবশ্য আছে, মেরে শেষ করা যায়নি।
আরও পড়ুন
সিঙ্কোনা-কাহিনি
মহানদীর পাশে, গুলমা নদীর ধারে, কিছু দূরের খাপরাইল এলাকায় পুরোনো মেচ বসতির কয়েকটা এখনো টিঁকে আছে। উত্তর পলাশ, দক্ষিণ পলাশ, বেতগাড়া, মানসারা জোত। সে সব গ্রামে যাবার, মেচদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেছে। অভ্যাসবশত, মেচ মহিলারা আর বয়ষ্ক পুরুষেরা বনে ঢোকেন। শাকপাতা, মাছ নিয়ে আসেন। অল্পবয়সী ছেলেরা সেগুন গাছ কেটে শিলিগুড়ি বাজারে বিক্রি করে। আশপাশের আর দশটা গ্রাম থেকে মেচ গ্রামের তফাৎ করা যায় না। মেচরা নিজেদের পরিচয় দেন হিন্দু বলে, পুরোনো লোকপ্রথা নিয়মকানুন কিছুই আর কারুর মনে নেই। অবশ্য গ্রামে গ্রামে ইদানিং লোকগান, লোকনৃত্যের দল হয়েছে, সরকারি উৎসবে গিয়ে ফসল রোযার, কাটার, মাছ ধরার নাচগান দেখানো হয়। গুলমা নদীর পাড়ে বেতগাড়া মেচ বস্তির পাশের শালবনে কাঁটাতারে ঘেরা সাফারি পার্ক, সেখানে শহরের লোক খোলা জায়গায় বাঘ দেখতে আসে।
Powered by Froala Editor