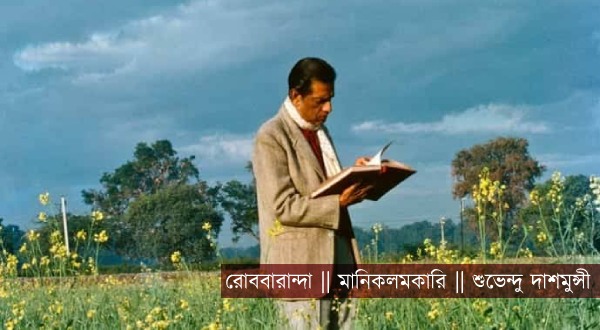বরাহনগর বা বরানগরের আনন্দগোপাল ভট্টাচার্য আর তার তিনজন বাঙালি ফৌজি সহযোদ্ধা গেছিলেন— গেছিলেন বললে ভুল হবে, চেষ্টা করেছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর আজাদি সেনাদের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও আরও বেশি তীব্রতর করবেন। এই ভরসা আর বিশ্বাস নিয়ে বরানগরের বড়াল পাড়ার আনন্দগোপাল ভট্টাচার্য আর তাঁর বন্ধুরা— মানে ব্রিটিশ সরকারের সামরিক বাহিনীর বন্ধুরা সৈন্যবাস— তাঁবু থেকে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন কৌশল করে। কী সেই ট্যাকটিকস— কৌশল, তা তো বলা হয়েছে আগেই। জুম্মা খাঁ আর বাচ্চি খাঁ— দুই পাঠান সেনাকর্তার দুর্ব্যবহার, অত্যাচার, স্পাইং মনোভাব— সব সময় চোখে চোখে রাখা ইত্যাদি পেরিয়ে— এড়িয়েও, তাঁরা— সেই তিন তরুণ বাঙালি সিপাহী কীভাবে কীভাবে যে পৌঁছে গেছিলেন কোহিমার গহীন অরণ্যে আর অবশেষে ফল তো নেহাতই শূন্য, কারণ রাতের গভীরে মিলিটারি হাসপাতাল থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে, কোনোভাবে বেরিয়েছিলেন তাঁরা, খুবই আস্তে, চুপি পায়ে, হাসপাতালে তখন তেমন প্রহরাই বা কোথায়? যা, যেটুকু পাহারাটাহারা— সবই প্রায় ভারতীয় সিপাহী, ভারতীয় সৈন্য, ফলে বাধা যে খুব আসবে, এমন তো নয়। সে রাতে ঝমঝম ঝমঝম ঝমঝম বৃষ্টি ছিল। বজ্র-বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। চারপাশে জলের শব্দ, বৃষ্টি পতনের শব্দ— নিরঙ্কুশ বৃষ্টিরই পতন চতুর্দিকে। রাতে বৃষ্টি পড়ে চলেছে আকাশ সাদা করে। এমন একটা পরিবেশে ‘এমনই বরষা ছিল সেদিন’ গাইবার কোনো পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। হয়ওনি। বরিষণ ধারা, বজ্রপাতের শব্দ, অস্থায়ী সেনা হাসপাতাল থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে এসে তখন তো ঘোর বর্ষণে ভিজতে থাকা, হঠাৎই আনন্দগোপাল ভট্টাচার্যর পায়ে কী যে কী ঠেকল, তখনই প্রবল বাজের আলোয়— বজ্রপাত ও চিকুর হানার আনন্দগোপাল দেখতে পেলেন এক সিপাহী— তিনি শিখই হবে ধর্মে, কারণ তাঁর মাথার পাগড়ি গালের কালো দাড়ি তো তেমন কথাই ব্বলে যাচ্ছে। তো সেই মিলিটারি ইউনিফর্ম— ফৌজি পোশাক পরা শিখ যেন বা পাহাড়-পর্বত হয়েই শুয়ে ছিলেন অস্থায়ী সামরিক হাসপাতালের বাইরে। মৃত মানুষ কথা বলে না। বলতে পারে না তার নাম, বয়স, জাত-পাত মজহব, তারই মধ্যে এই শিখ সিপাহী যেন বা কোনো অকুল প্রস্তর। যো বোলে সো বোলে নিহাল/ জয় সৎশ্রী অকাল—’ এই উচ্চারণের মধ্যে দিয়েই যেন এক শিখবান্দা ঝাঁপিয়ে পড়েন রণস্থলে। তাঁর এই রণধ্বনি যেন মুছে দেয়, মুছে দিতে থাকে সমস্ত ভয়, ত্রাস। শত্রু— দুশমনের বুকে ধরায় আতঙ্ক— কাঁপুনি। ধ্বংসের ভয়ে মৃত্যুভয়ে অস্থির, হয়ে ওঠে শত্রু শিবির। ‘ওয়া গুরুজিকা ফতে’ বা ‘বাহে গুরুজিকা ফতে’ এরকম রণচিৎকারও যেন ভেসে উঠতে থাকে শিখ ভাইদের মুখে মুখে, রণক্ষেত্রে লড়তে লড়তে আজও। পঞ্চ ক— কড়া, কঙ্খা, কাঞ্ছা, কেশ, কৃপাণ, এই রকমই পাঁচটি ধার্মিক চিহ্ন। আর এইসব ধর্মগত চিহ্ন কখন যেন হয়ে উঠতে থাকে জীবনগত চিহ্ন। শিখ-ধর্মের সেই সব নিত্য অভ্যাস লেখ নিয়ে শুয়ে আছেন ব্রিটিশ আর্মির সর্দারজি— সিপাহী কত, কত, কত দূর থেকে পাঞ্জাবকে পুত্তর— পাঞ্জাব— অখণ্ড পাঞ্জাবের সন্তান চলে এসেছে— ভরতি হুয়া হ্যায় ফওজমে, সে হয়তো কৃষক পরিবারেরই সন্তান। গেঁহু— গম ফলানো পরিবার। সঙ্গে বাজরা, মকাই, সর্ষে। মক্কি কি রোটি অওর সরষোঁকা শাগ— মকাইয়ের রুটি আর সর্ষে শাক। সেই সঙ্গে দমভর— জি ভর ভঁয়স কা দুধ— মোষের দুধ আর লস্যি। দুধ আর মোটা মালাই— সর দেওয়া চায়— চা। এভাবেই তো কৃষক জীবন কিষানকে জিন্দগি। অন্যরকম হলেও মনে পড়ে কী ‘মাদার ইন্ডিয়া’ ছবিটির কথা? নার্গিস, সুনীল দত্ত, রাজকুমার। এই মাদার ইন্ডিয়া অবশ্য ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের বেশ কিছু পরে তোলা ছবি। সেই সিনেমায় হয়তো বা তথাকথিত ‘নেহরুভিয়ান সোসালিজম’— পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু মার্কা ‘ফেবিয়ান সোসালিজম’-এর জয়গান। কল্পকথা। রজনী পাম দত্ত বা রজনী পালমে দত্ত— তাঁর প্রবর্তিত তত্ত্ব ও প্রয়োগ, নেহরুজি— পণ্ডিত নেহরুর সাধের সমাজতন্ত্র— ‘সোসালিস্টিক প্যাটার্ন’— সোসালিস্তিক প্যাটার্ন অফ আ ক্যাপিটালিস্টিক সোসাইটি। পঞ্চাশের দশকে তৈরি হওয়া বহু বোম্বাইয়া ছবিতেই তো নেহরু— পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর স্বপ্নের ‘সোসালিস্টিক প্যাটার্ন’ উচ্চারিত হচ্ছে। বিশেষ করে রাজ কাপুর সাহাবের ছবিতে— আর কে স্টুডিওর ব্যানারে তৈরি সিনেমা, সেইসঙ্গে সঙ্গে ‘জেমিনি’, ‘নবকেতন’। আমায় মৃণালদা— মৃণাল সেন একবার বলেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে সত্তর দশকেও সবাই মনে করে ইন্ডিয়ান সিনেমা— ইন্ডিয়ান ইয়ুথ মানেই রাজ কাপুর সাব— ‘আওয়ারা হুঁ’— ‘আওয়ারা হুঁ’— সেই সামান্য গোটানো ফুলপ্যান্ট। মাথায় টুপি। কাঁধে লাঠি আর পুঁটলি সমেত— ‘মেরা জুতা হ্যায় জাপানি/ ইয়ে পাতলুন ইংলিশস্তানি/ শর পে লাল টোপি রুশি/ ফির ভি দিল মে হিন্দুস্থানি…।’ গুটিয়ে নেওয়া ঢোলা ফুল প্যান্টের বাইরে বেরিয়ে থাকা রাজ কাপুর সাহাবের ফরসা বললে কম বলা হয়, অতি ফরসা পা, সঙ্গে ভোলেভালি নার্গিস। পৃথ্বীরাজ তনয়, রাজ কাপুর ও সিনেমায় ভোলেভালাই— নিতান্ত সুবোধ, সরল বালক, অথচ বাস্তব জীবনে প্রেমে, শরীরী খেলায় এক অনন্ত প্রতিভাধর যেন। নার্গিস, নার্গিস। বৈজয়ন্তীমালা, পদ্মিনী। সেসব যেন রঙিন বেদনাবিধুর দিন। রাজ সাহাব— রাজ কাপুর সাবকে নিয়ে কত কথাই না লেখার আছে। আপাতত সেখানে ইতি দিয়ে আজাদি সেনার সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দিতে চার বাঙালির যাত্রাপথের কথাতেই ফিরি। সেই সৈনিক সর্দারজির লাশ, প্রবল থেকে প্রবলতর বৃষ্টিতে ঘামাসান। যাত্রাপথের কথাতেই ফিরি। কোহিমার জঙ্গল পথে ভিজতে থাকা শিখ সিপাহির লাশ, বরিষণ ধৌত ফোজিউর্দি। কোহিমার আকাশ থেকে অনবরত বারিপাত। কাদা, জল লতপথ সিপাহীর প্যান্ট, শার্ট, পায়ের জুতো, মোজা। সেই আলিশান লাশের গায়েই ঠোক্কর খেয়ে বরানগরের আনন্দগোপাল প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি। খানিকটা ভয়। তার সঙ্গে সঙ্গে লাশ-সংঘর্ষের ফলাফলে যেটুকু ঘেন্না ও বিবমিষা। তাঁর তিন মিলিটারি সহকরও সেই একই সংশয় আর ভয়ের মধ্যে। ঘন বৃষ্টির সেই রাত। চারপাশে বজ্রপাতের শব্দ, ব্যাঙের ডাক, হয়তো বা সাপের ব্যাঙ ধরার করুণ শব্দও। সেই শিখ সিপাহীর শবে ধাক্কা খেয়ে, ওফ, নাকি উঃ রে বাবা বলেছিলেন, আনন্দগোপাল ভট্টাচার্য, তা জানবার জন্য কোনো সাক্ষ্য আর মজুত নেই আমাদের সামনে। কিন্তু এই ‘ওফ’, ‘উফ’ বা ‘উঃ রে’ প্রায় বাতিল হয়ে গেছে আমাদের জীবন থেকে। মূলত টেলিভিশন— বিজ্ঞাপন প্রভাবে। কারণ টিভি অ্যাডের ব্যথা উপশমের বাম আমাদের শেখাল ‘উফ’, ‘ওরে বাবা’, ‘উঃ’-র বদলে ‘আউচ’ বলতে। ব্যথা পেলে— ধাক্কা লেগে ব্যথা ‘আউচ’। এভাবেই মন্দিরের ভাষা, মদের ঠেকের ভাষা, বেশ্যাবাড়ির ভাষা, জেল খানার ভাষা— সব— সব কিছু সাধারণের উচ্চারণ থেকে বদলে বদলে যায়। সৈনিকদেরও ভাষা আছে। ‘প্রহার’, যে সিনেমাটিতে নানা পাটেকার ছিলেন মূল চরিত্রে, কমান্ডো ট্রেনিংয়ের একটা ব্যাপার ছিল সেই ছবিতে। স্পষ্ট আর ঠিকঠাক করে বললে ‘প্রহার’ তৈরিই হয়েছে কমান্ডো ট্রেনিং নিয়ে, সেই ছবি কিছু ভাষা ছিল একে অন্যকে সম্বোধন। ‘ঘাস-বিচালি-ঘাস— ঘাস-বিচালি-ঘাস’— লেফট অ্যান্ড রাইট, ‘লেফট অ্যান্ড রাইট’, দায় না— বাঁয়া, বাঁয়া দায় না, ‘আচ্ছা আচ্ছা— শুয়ার কা বাচ্চা’— এমন এক কথ্য ঝঙ্কার চালু ছিল ব্রিটিশ ভারতে, সামরিক বাহিনীর ভেতর। বিশেষ করে পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে। ‘আচ্ছা আচ্ছা, শুয়ার কা বাচ্চার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ‘আচ্ছা, আচ্ছা গাধা কি বাচ্চা’-ও চালু ছিল সেই ব্রিটিশ জমানায়। সাধারণ সিপাহীদের— তাঁরা যদি ভারতীয় হতেন, তাহলে যুদ্ধে ‘কামানের খোরাক’— ‘ফডার অফ দ্য ক্যানন’ হওয়া ছাড়া কোনো উপায়ই তো ছিল না। সাধারণভাবে প্রায় সব দেশের সোলজারদেরই একই দশা প্রায়। অস্বাস্থ্যকর, ভেজা ভেজা পরিখা— ট্রেঞ্চে মাসের পর মাস, পরবর্তী সময় বাঙ্কারে, সেখানেও একই দশা। ভারি বোমা বর্ষণে বুউউ— বুউম শব্দে, কাঁপুনি তরঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠছে সমস্ত বাঙ্কার। মানে মাটির অনেক, অনেক নিচে বাঙ্কার, অনেক নিচে বাঙ্কার, গভীর গভীরতর প্রদেশে পৌঁছে যাচ্ছে ভারী বোমা বর্ষণের তরঙ্গ। কেঁপে কেঁপে উঠছে, সব কিছু। এরকম বাঙ্কার গভীরেই তো থাকত ফুয়েরার— অ্যাডলফ হিটলার। তার প্রণয়িনী এভা বা ইভা ব্রাউন সহ। আর হিটলারের অতি প্রিয় কুকুর ব্লন্ডি। শেষ পর্যন্ত এভা বা ইভা ব্রাউনকে বিবাহ করে হিটলার। তারপর আত্মঘাতী হয় দুজনে মিলে। ব্লন্ডিকেও হত্যা করা হয়, গুলি করে। হিটলারের সহযোগীরা গোয়েবলস, মার্শাল, গোয়েরিং, আইখম্যান, হিমলার, রিবেনট্রপ, রোমেল— সকলের পরিণতিই প্রায় আত্মহনন। রোমেল— ভেজার্ট ফক্স— মরু শৃগাল রোমেলকে আত্মহত্যায় বাধ্য করে হিটলার। আফ্রিকায় রোমেলের পরাজয়। গোয়েবলসও তো আত্মহননের পথেই যায়— সপরিবারে বাঙ্কারের মধ্যে, হিটলারের বাঙ্কার। সমস্ত জার্মানি যখন প্রবলভাবে সোভিয়েত রেড আর্মির গোলায় ছিন্নভিন্ন, গোটা বার্লিন জ্বলছে ব্রিটিশ বোমারু আক্রমণে, ধ্বসে পড়ছে বড়ো বড়ো তৃতীয় রাইখ-চিহ্ন— স্বস্তিকা, ঈগল। রাস্তা জুড়ে মৃতদেহ। খাদ্য নেই। আলো নেই। জল নেই। তারই মধ্যে হিটলারের বাঙ্কার গভীরে বিপুল পানভোজন, খাওয়া-দাওয়া, গোপন আতঙ্কময় ফুর্তি। ভাবখানা এরকম— যা হচ্ছে হোক বাইরে, আমরা তো বেশ আছি, ঠিকই আছি। থোড়াই কেয়ার আমাদের। হিটলারের আতঙ্ক ছিল যদি সোভিয়েত লাল ফৌজের হাতে ধরা পড়ি, তাহলে তো একবারে চোদ্দটা বেজে গেল। এই অবস্থার মধ্যেই ধীরে ধীরে আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে হিটলার ও তার সহযোগীরা। সাবমেরিন— পনডুব্বি— ডুবোজাহাজ— যে নামেই ডাকি না তাকে, নটিক্যাল মাইলের হিসাব, ইউবোট আর শত্রুপক্ষের রণতরীর নজর এড়িয়ে সেই যে যাত্রা, গভীর জল তল দেশ— সমুদ্রের— সমুদ্র গভীরের আরও নানা জীবনচিহ্নকে সঙ্গে নিয়ে, যেমন সাগরতলের প্রবালকুঞ্জ, ডুবে যাওয়া ভাঙা জাহাজ, সমুদ্রের তলদেশে থাকা বালিভূমি, সি কিউকুমবার অক্টোপাস, তারামাছ, স্কুইড, নানা ধরনের রঙিন মাছ, স্টার ফিশ, বিভিন্ন প্রজাতির ছোটো-বড়ো তিমি মাছ, সে ব্লু হোয়েল— নীল তিমি হতে পারে, হতে পারে পিঠে কুঁজওয়ালা তিমি, বিভিন্ন প্রজাতির শার্ক— হাঙর, তার ভয়াবহতা, সাবমেরিন চারপাশে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যে সব নৌবাহিনীর জনেরা সাগরতলে থাকে সাবমেরিন যাত্রায়, তাদের শরীর-স্বাস্থ্যের ওপরও নানা ধরনের চাপ পড়ে। এসব নিয়ে লেখালেখিও হয়েছে বিস্তর— অন্তন বিশ্ব মহাযুদ্ধকালীন সাবমেরিনে থাকা নৌসেনা ও অফিসারদের নিয়ে। এসব নিয়ে সিনেমাও হয়েছে পরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পৃথিবীতে ঠান্ডা যুদ্ধ— কোল্ড ওয়ারের কালে তখন তো সমুদ্রজলের নিচে মাসের পর মাস সোভিয়েত-আমেরিকান টহলদারি সাবমেরিন। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ঘাঁটি রক্ষা করছে। তখন তো চারপাশেই নানা ধরনের রাজনৈতিক টানাপোড়েন। সোভিয়েত ব্লক বনাম মার্কিন ব্লক। সেটো-সিয়াটো, ন্যাটো, বিপ্রতীপে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত পূর্ব ইউরোপ। সবটাই সামরিক চুক্তি, সামরিক জোট। ভারত প্রথম থেকেই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পক্ষে। কোনো সামরিক জোটেই তো সে নেই। বান্দুং সম্মেলন ইত্যাদির কথা নতুন করে বলার নয়। শেষ পর্যন্ত আনন্দগোপাল ভট্টাচার্য আর তাঁর তিন সৈনিক বন্ধু পৌঁছতে পারেননি আজাদ হিন্দ বাহিনীর কাছাকাছি। পথেই ধরা পড়েছিলেন তাঁরা। তারপর বিচার। বিচার গড়াতে গড়াতে দেশে, দেশের বাইরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওপর ক্রমাগত চাপ। ফলে কোর্ট মার্শাল হয়ে হয়েও তো হল না শেষ পর্যন্ত। মুক্তি পেয়ে গেলেন তাঁরা সবাই। সে এক অন্য ইতিহাস। মুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা, এটাই খবর শেষ পর্যন্ত। শাস্তি দিতে পারেনি ব্রিটিশ প্রশাসন তাঁদের। এই তো শেষ হয়ে গেল ইতিহাসের একটা পর্ব। এবার বলব ভাষা নিয়ে, আগামীবারের ‘মুছে যায়?’-তে। এই বলাবলিটুকুর সামান্য আভাস দিয়েছি এই লেখারই মধ্যে। বলব জেলখানার ভাষা নিয়ে, লিখব বেশ্যাবাড়ির ভাষা নিয়ে। তার সঙ্গে সঙ্গে লিখতে থাকব মন্দিরের ভাষা, মন্দিরের ভাষা বলতে মূলত ছড়িদার, পালাদার পাণ্ডাদের কথা ভোকাবুলারি। সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানঘাটের ভাষাও। কথায় কথায় কত কথা যে বদলে বদলে যায়। সুকুমার রায় হয়তো একেই বলেছিলেন, ‘কথায় কাটে কথ্র প্যাঁচ।’ আশ্চর্য সেইসব লাইন ধরে এগোতে এগোতেই আমরা হয়তো কখনও কখনও পেয়ে যাই পাউরুটির আর ঝোলাগুড়ের লাইন। সব চেয়ে ভালো যা সুকুমারীয় গদ্যে। এই যে ভাষা পথ, ভাষাযাত্রার কথা বলব, তার সঙ্গে অবশ্যই উঠে আসা উচিত প্রাচীন সব সরাইখানার কথা যে সরাইখানায় আসতেন ভাগ্যান্বেষী বণিক, যোদ্ধা-যুদ্ধ ব্যবসায়ী, যারা পেশাদার— পেশাগতভাবেই যুদ্ধকে নিয়েছে, এখানকার— এই সময়কার ভাড়াটে মার্সেনারি, সেই সরাইখানার ভাষা অবলীলায় মিশেছে মানবজীবন রহস্যে। মানবপথের ভাষা সৌন্দর্য, ভাষা আনন্দ, ভাষা বিষাদে। সে এক অদ্ভুত যাত্রাপথ, সেই সরাইখানার ভাষা সত্যি সত্যি আর এখন কুড়িয়ে পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আজাদি সেনার ‘কদম কদম বঢ়ায়ে যা—’ অথবা ‘জয় হিন্দ’, নয়তো ‘চলো দিল্লি, দিল্লি চল—’ এই রণধ্বনির মধ্যে দিয়ে জীবন পর্যায়ের বিবিধ তরঙ্গ তুলে সেই ভাষা আমাদের প্রাণিত করে, অনুরণিত করে। জীবন সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে সেই ভাষাচিহ্ন যেন পৌঁছে যেতে থাকে দূরে, সুদূরে। কাছে। বারবারই মনে হয়ে থাকে যদি সত্যি সত্যি সেই সরাইখানার ভাষাকে উদ্ধার করতে পারতাম, নিজ হাতে, নিজস্ব ভাষায়, নিজস্ব জীবনপঞ্জিতে। এক বা ইক আধুরি কহানি নয়, পূর্ণ, পূর্ণতর কাহিনি কোনো। ঘামে, বিষাদে, কান্নায়, অপরূপ যাত্রাখণ্ডে সে বড়ো মোহ, বড়ো মোহ, নিত্য নবীন ও নিত্য ভাবনাময়। প্রাচীন সরাইখানার নিভু দীপ, গণিকার আসব ঝঙ্কার, কামতাড়িত পুরুষের জীবন-জিয়ল-তরঙ্গ, সব মিলিয়ে নিশ্চিত বা অনিশ্চিত কোনো আলোছায়া। দিলের রবাব, শূলপক্ক মাংসের পোড়া পোড়া ঘ্রাণ, সময় এসেছে বিজয়ী অথবা বিজেতার বেশে।
Powered by Froala Editor