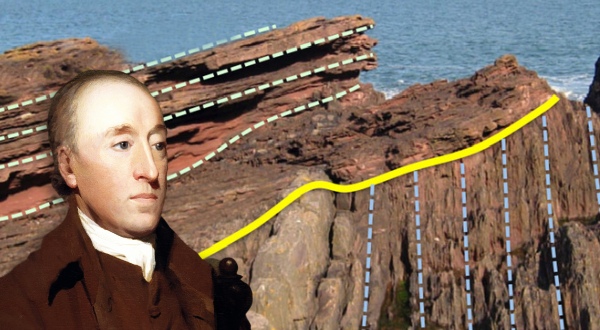ইলাহাবাদে হোলিতে— হোলির হুড়দঙ্গে খুন-খারাবা— হত্যা-পাল্টাহত্যা— খুন— ‘ঢের কর দিয়া’— ‘শেষ করে দিয়েছি’— এই ঘটনা পরম্পরা ষাট-সত্তর-আশি— ছয়, সাত ও আট দশকে অবধারিত। তার রেশ চলে এক বছর ধরে। কাপড়া ফাড়কে উসকো নাঙ্ঘা কর দো— নাঙ্গা করে দাও, ল্যাংটো কর— এই ব্যাপারটাও খুব ছিল। বিশেষ করে সে-সকম ‘লেডিস মার্কা’ কাউকে পেলে তো আর কোনো কথাই নেই। তার হয়ে গেল। পারলে একদম পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে তার জামা-কাপড় ছিঁড়ে তাকে ল্যাংটো— নাঙ্ঘা বা নাঙ্গা করে দেওয়া একেবারে। ‘হোলিকা’— হোলির আগের রাতে বড়ো বড়ো কাঠের গুঁড়ি— লগ জ্বলে ‘হোলিকা দহন’-এর যে ‘নিয়মকানুন’, সে ব্যাপারে চাঁদা— চান্দা না দিলে তখন যিনি চাঁদা দিলেন না, তাঁর বাড়ির সদর দরজায় অবধারিতভাবে কাঁচা গুয়ের হাঁড়ি— একেবারে গু ভর্তি পোড়া মাটির হাঁড়ি পটকে দেওয়া চাঁদা— চান্দা না দেওয়ার ফলাফল হিসাবে। কলকাতার গা লাগোয়া মফঃস্বলে পুজোর চাঁদা না দিলে, তাদের বাড়ির দরজাতেও মলভর্তি টব বা হাঁড়ি ফেলা, এমনটি হত। বালিতে রক্ষাকালী পুজোর চাঁদা ‘ঠিকঠাক’ পুজো কমিটির দাবি অনুযায়ী না দেওয়ায় আমাদের বালির বাড়ি— ৫৯/১৩ শান্তিরাম রাস্তার বাড়িতে পচা গু পোঁচড়া মেরে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উফ, সে কি খোয়ার বা ভয়াবক দুর্গন্ধ। সেই বিষ্ঠার ভেতর আবার মেশানো হয়েছিল গঙ্গার কাঁকড়া। গঙ্গাজলের কাঁকড়া মানে সাদা সাদা বাচ্চা। সেই মলমাখা কাঁকড়া আবার চলতে আরম্ভ করল ‘মুক্তি’ পেয়ে। ব্যস, সমস্ত ঘর-বাড়ি-দালান, রান্নাঘর, ঠাকুরঘর, বসার ঘর, শোয়ার ঘর, চানঘর— সব গুয়ে কাঁকড়ায়— গু মাখা কাঁকড়ায় একেবারে ‘বৈকুণ্ঠ’, কারণ ঐ ভয়ানক গ্যাস সমেত মলের ভেতর যে কর্কট-শাবকরা বাঁচল তারা তো তাদের পায়ে পায়ে বাড়ির সর্বত্র— সমস্ত জায়গায়। কথায় বলে, হাগা পেলে বাঘার ভয় থাকে না। অর্থাৎ পায়খানা পেলে, তখন আর কোনো ভয়ই থাকে না। সংকোচ, লজ্জাও না। আমাদের বালির বাড়িতে ৫৯/১৩ শান্তিরাম রাস্তায় একজন পোস্টম্যান— ডাক পিওন আমাদের পায়খানা ব্যবহার করতে চান ভরা গরমের দুপুরে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে আমাদের পায়খানা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। আর তিনি তা ব্যবহার করে ‘পেট খুলাসা’ করার পর খুব বড়োসড়ো রিলিফ পান, এমন সকৃতজ্ঞ হাসি নিয়ে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যান। তখন ডাকপিওন বা পোস্টম্যানদের বড়ো ঝোলা বা ব্যাগ থাকত চিঠি রাখার জন্য। ইনল্যান্ড, এনভেলাপ, পোস্ট কার্ড মানি অর্ডার, টেলিগ্রাম মানিঅর্ডার, টেলিগ্রাম— এমন কত কি! এখন— গত কয়েক বছর হল ডাকবিভাগের সেই গুরুত্বই তো আর নেই। ধীরে ধীরে মেরে ফেলা হচ্ছে ভারতীয় ডাক বিভাগ— ইন্ডিয়ান পোস্টাল ডিপার্টমেন্টকে। খুব পরিকল্পনা মাফিক হচ্ছে এই ‘কাজ’। মূলত ইডি স্টাফ দিয়ে কাজ করানো হয়। লোক নেই। অনেক অনেক শূন্যপদ। ধীরে ধীড়ে সমস্ত ডাক বিভাগ— ভারতীয় ডাক বিভাগকেই তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বহু বছর ধরে। লেটার বক্স— লাল রঙের ডাকবাক্স ক্রমশ অ্যান্টিক পিস হয়ে যাচ্ছে। কমেও যাচ্ছে ধীরে ধীরে। দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটের ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিট-এ ঢুকতে গেলে ডানদিকে বড়ো দেওয়ালে ঝোলানো থাকত একটি লাল রঙের ছোটো ডাকবাক্স। প্রায় বছর পনেরো সেই বাক্সটি নিরুদ্দেশ। নেই। কত চিঠি ফেলে এসেছি সেখানে— তার গভীরে, পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ড, এনভেলপ। সে যেন গত জন্ম, নাকি তারও আগের কোনো জন্মকথা, জন্মদাগ। আমার স্মৃতিতে লেটারবক্স— লাল রঙের বড়ো লেটারবাক্স— চিঠি বাক্স— ডাকবাক্স সেই ধর্মতলায় কলকাতা কর্পোরেশনের সামনে, ফুটপাথের ওপর। আর ধর্মতলাতেই, মানে এসপ্ল্যানেড ইস্টে কে.সি. দাসের পাশে বড়োসড়ো পোস্টাপিস আর তার সামনে লাল ও সবুজ ডাকবাক্স। একসময় হাওড়া স্টেশনের সেই অতিবিখ্যাত বড়ো ঘড়ির পাশেই আরএমএস। ডাকবাক্স, প্রায় দেওয়ালের সঙ্গে ঘেঁষা চিঠি ফেলার জন্য অতি বড়ো হাঁ মুখ। আমার পিতৃদেব অমরনাথ রায় ছিলেন রেলচাকুরে। হাওড়া রুট রেল কেবিন-এর কেবিন এএসএম। তো বাবা তখনকার অনেকেই যেমন পোস্টকার্ড বা ‘পোস্টোকার্ড বিলাসী’, তেমনই ছিলেন। পোস্ট কার্ডের মাথায় ‘ওঁ’ লিখে তিনি শুরু করতেন। চিঠিতে— চিঠির মাথায় বাম দিকে, মানে আমার ডান দিকে তারিখ। চিঠির বাঁ দিকে। যেখান থেকে চিঠি লিখছেন, সেই জায়গায় নাম। বাবা নিয়মিত চিঠি লিখতেন তাঁর দিদি কিরণপ্রভা ভট্টাচার্যকে। ছোটো শ্যালিকা নমিতা ভট্টচার্যকে। হাওড়া আরএমএস-এ চিঠি পোস্ট করলে সেই চিঠি পরদিন ৩৪/বি তেলিপাড়া লেনে তাঁর সুন্দরী ছোটো শ্যালিকার ঠিকানায় পৌঁছে যায়। নয়তো তাঁর আড়াই বছরের বড়ো দিদি কিরণপ্রভা ভট্টাচার্যের কাছে— ৪০/১এ জয়নুদ্দিন বা জৈনুদ্দিন মিস্ত্রি লেনে। ছোটো শ্যালিকা শ্যামপুকুর, তেলিপাড়া লেনে, ‘টাউন স্কুল’-এর কাছাকাছি। দিদি চেতলায়। বড়ো শালি উষারানি ভট্টাচার্য ১৬/১ ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিট-এ, কালীঘাট— দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটে। কলকাতা-২৬। এই বাড়ির দু-দুটো ঠিকানা— ১৬/১ ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিট আর ১ এ মুখার্জি পাড়া লেন। এই কথা আগেও লিখেছি, একই বাড়ির দু-দুটো ঠিকানা। বাবা ইলাহাবাদে রেণু মাসির— রেণুকা ভট্টাচার্যর কাছে হাওড়া আরএমএস-এ চিঠি পোস্ট করলে, তা ইলাহাবাদের পত্রপত্রিকা— ডান বাক্সে পৌঁছে যেত তিনদিনে। হ্যাঁ, তিন থেকে চারদিন লাগত বড়োজোর। আর মানি অর্ডার পৌঁছতে পাঁচদিন। অর্ডিনারি মানি অর্ডার— এমও— খুব বেশি হলে পাঁচদিন— কলকাতা থেকে ইলাহাবাদে। আর টিএমও— টেলিগ্রাম মানিঅর্ডার হলে তিন দিন— একদম হিসেব বাঁধা। আমি তিন নয়া পয়সা, পাঁচ নয়া পয়সা, দশ নয়া পয়সা, পনেরো নয়া পয়সার পোস্টকার্ড দেখেছি। ব্যবহার করেছি দশ নয়া পয়সার ইনল্যান্ড-লেটার-অন্তর্দেশীয় পত্র, তারপর তা বেড়ে পনেরো নয়া পয়সা, পঁচিশ নয়া পয়সা। চিঠি লিখে খামের ভেতর পুরে দেওয়ার অশোকস্তম্ভ মার্কা লিফাফা এনভেলপ পঁচিশ নয়া পয়সা, পরে পঞ্চাশ নয়া পয়সা। এছাড়া ছিল বিদেশি চিঠি লেখার জন্য এয়ারোগ্রাম। পোস্ট কার্ডে অশোকস্তম্ভ, পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন— ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাড লাল ক্রিকোণের সাদা-কালো ছবি। ‘ছোটো পরিবার, সুখি পরিবার’। ‘সুখ কা রাজ হ্যায় ব্যস দো বাচ্চে/ মুখ কি নিশানি লালা ত্রিকোণ/ লাল ত্রিকোণ লাল ত্রিকোণ…’। এই দুই শ্লোগান ছাড়া কেবল ছবি পোস্টকার্ডে। তাছাড়া কোনার্ক মন্দিরের পাথুরে অশ্বমূর্তি, বাহারি ময়ূর-মূর্তি— তা কোনো ফিল্মোৎসবের ছবি হবে, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। শুরু করেছিলাম দোল, রং-উৎসব— হোলি দিয়ে। আমার গর্ভধারিণী গায়ত্রী রায় বলেছেন, তাঁদের দ্যাশের বাড়ি ‘অখণ্ড বঙ্গের ফরিদপুরের আকসা— ভোজেশ্বরে দোলের আগে আগে পাকা, সরু তলতা বাঁশ কেটে নিয়ে তারপর তার এক গাঁট থেকে অন্য গাঁটের মাপটুকু নিয়ে পিচকিরি— রং খেলার পিচকিরির খোল তৈরি করা হত। লোহার কীলক— ধারাল পেরেক উনোনের আঁচে একেবারে লাল টকটকে গরম করে, তারপর সেই ‘নোকিলা’ ধারাল, গরম পেরেক দিয়ে পিচকিরির মুখের ফুটো তৈরি করা হল। এবার নিচের দিকে রঙ আর জল টানার জন্য বাঁশেরই হ্যানডেল, তাতে পুরনো ন্যাকড়া দিয়ে তৈরি ওয়াশার। এসবই করতেন গায়ত্রী, ঊষা, অচিন্ত্য, খগেশদের দাদা দীনেশদা— বড়দা দীনেশ চন্দ্র রায়। তিনি শশধর আর হরিপদ রায়ের বড়ো ভাই শ্রীরাম রাএর বড়োখোকা— বড়ো পুত্র। দীনেশচন্দ্র ছাড়া ঊষা, গায়ত্রী, অচিন্ত্য, খগেশদের লাবড়াদা, কউয়্যাদা— কচু রায়, সারদা শাণ্ডিল্য— সারদা কাকা— কুট্টি কাকা— এঁরা সবাই ছিলেন, থাকতেন এই পিচকিরি নির্মাণে। এক হাতের মতো লম্বা। গোলাই— পোক্ত, সরু বাঁশের ডগা যেমন হয়, তেমনই। আর তা থেকেই পিচকিরি— বাঁশের পিচকিরি। এই ছবি ১৯৪০-৪২-এ যেমন, তেমনই ১৯৩৭-৩৮-এও। সব বাড়িতে তৈরি— হোম মেড। রং বলতে আর্থ কালার— প্রাকৃতিক রং। কৃষ্ণকলি বা কেষ্টকলি ফুল গাছের সবুজ সবুজ পাতা থেঁতো করে হরিৎ রং। তারপর জবা ফুলের পাপড়ি, কুঁড়ি দিয়ে লাল রং, হলুদ হলুদ ফুল, তা থেকে হলুদ রং। মাটির হাঁড়ির কালো— ভুষো দিয়ে কালো রং। এই ছবি তখনকার অখণ্ড বঙ্গের পুবভাগে, পূর্ব বঙ্গে। ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশালে দোলের আগের রাতে বুড়ির ঘর পোড়ানো চালবাটা দিয়ে তৈরি মেড়া বা ভেড়া— মেঢ্রাসুরের প্রতীক। সেই ঘর— ছোটো ঘর তৈরি হত দহনের জন্য। দাহর জন্য। দহন দহন দহন। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা-কাঁসরের সঘন বাদন। ঘড়ি-ঘণ্টা— কাঁসার তৈরি বড়ো গোল একটি ভারি জিনিস এই ঘড়ি-ঘণ্টা, তাতে কাঠের শক্তপোক্ত ডাণ্ডা দিয়ে ছন্দে বাজানো— ঢং ঢং ঢং ঢং। কাঁসরের শব্দ কিছু তীক্ষ্ণ। ঘড়ি-ঘণ্টার ওপর কাঠের যে বেড়ন, তার প্রহারে চমৎকার, ছন্দময় শব্দ উঠে আসে। আমাদের স্কুল বালি জোড়া অশ্বাত্থতলা বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু ও সমাপ্তির ‘বেল’ বাজতে ঘড়ি-ঘণ্টার ওপর ছোটো কাষ্ঠদণ্ড পিটুনিতে। ‘ওয়ার্নিং বেল’ বাজত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ক্লাস শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে। তারপর ক্লাস শেষ হলে ‘ফাইনাল বেল’— এই দুই বাদনে খুব স্বাভাবিকভাবেই মাত্রা ও ছন্দ স্বতন্ত্র ছিল। সেই চকচকে, ভারি, কাঁসার ঘড়ি-ঘণ্টাটি ঝুলে থাকত লোহার মজবুত ‘এস’ চেহারার আঙটায়। এই ঘড়ি-ঘণ্টাটি সাত দশকের প্রায় শেষ পর্বে চুরি হয়ে গেল, লোহার এস সমেত। ততদিনে আমি বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়-এর প্রাক্তন— প্রাক্তন ছাত্র— এক্স স্টুডেন্ট। কারণ ১৯৬৯ সালের মার্চে আমি হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিই। তার আগে টেস্টের পরই আমরা ‘সেই আপ’। ঘড়ি-ঘণ্টাটি তস্করে নেওয়ার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি বাতিল লোহার টুকরো— লোহার না বলে তাকে ইস্পাত বলাই শ্রেয়, তো সেই কালচে ইস্পাত খণ্ডটি বড়ো জোর হাত খানেক লম্বা। আর তাতে একটি বড়ো গোল হোল— গর্ত করা ছিল। লোহার মজবুত ‘এস’-এ ঝুলত সেই ইস্পাত খণ্ড। লোহার আর একটি হামানদিস্তা জাতীয় জিনিস দিয়ে তার গায়ে প্রহার করলে তখন ট্যাং-ট্যাং-ট্যাং ধ্বনি আসত উঠে। কাঁসার ভারি, চকচকে ঘড়ি-ঘণ্টা পেটানোর পর যে সমুদ্রতরঙ্গগর্জন সম গম্ভীর শব্দ— শব্দ না বলে তাকে নাদ বা নিনাদ বলাই বিধেয়, যেমন শঙ্খনিনাদ, তো সে যাই হোক ‘নাদ’-কে আবার ‘ব্রহ্ম’-র সঙ্গে জুড়ি দিয়ে ‘নাদব্রহ্ম’-ও বলা হচ্ছে, তো সেই যে ঘড়ি-ঘণ্টার শব্দ, তা নিনাদিত। তার সঙ্গে তুলনায় কীভাবে আসতে পারে ইস্পাত নির্মিত রেললাইনের টুকরো হেন, সেই বিকল্প ধ্বনিকেন্দ্র। মনে আছে আমাদের স্কুল বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়ে স্কুল বেল— স্কুল ঘণ্টা দিতেন নিতাইদা। গরম-বর্ষায়— গ্রীষ্ম-শীত ঋতুতে মর্নিং স্কুল ছিল ভোর সাড়ে ছটায়। শীতের দিনে সকাল সাতটা। আর ডে স্কুল— ক্লাস সেভেন থেকে ইলেভেন সকাল এগারোটা থেকে চারটে, বারো মাস। চাঁচর বা বুড়ির ঘর পোড়ানো— চালবাটা দিয়ে তৈরি পিটুলির ভেড়া বা মেড়া পোড়ানোর সময় ঘড়ি-ঘণ্টা, কাঁসর, ঘণ্টা— সবই বাজত। সেই আগুনে সমর্পিত হত চিনির মঠ, ফুট কড়াই, মুড়কি, আবির— কখনও কখনও। অখণ্ডবঙ্গের পূর্ব বঙ্গে চাঁচর, বুড়ির ঘর পোড়ানো, পিটুলি দিয়ে তৈরি মেড়া বা ভেড়া দাহন— যা কিনা মেঢ্রাসুরের প্রতীক, লিখেছি আগেই, সব ছিল। কিন্তু ন্যাড়া পোড়া ছিল না।
‘আজ আমাদের ন্যাড়াপোড়া
কাল আমাদের দোল
পুরনিমাতে (পূর্ণিমাতে) চাঁদ উঠেছে
বলো হরিবোল…’
দোলের ঠিক আগের দিন ন্যাড়াপোড়া। কাঁচাবাঁশ ভালো মাটিতে গর্ত করে ভালো করে পোঁতার পর তার সারা গা জুড়ে শুকনো কলাপাতার আস্তরণ। তার সঙ্গে ঝরা বাঁশপাতা। অন্য অন্য শুকনো পাতা। আমাদের বালির বাড়ি— ৫৯/১৩ শান্তিরাম রাস্তার যে বাড়ি, তার খুব কাছেই ছিল হারা ঘোষ-কেষ্ট ঘোষেদের বড়োসড়ো খটখটি বাগান। সেই খটখটি বাগানের ভেতর কলা গাছের বড়োসড়ো বাগান, বাঁশঝাড়, অনেক অনেক তাল গাছ, তাকে ঘিরে উল্লাসের তাড়ির ঠেক, নারকেল গাছের সারি, বেল গাছ, এছাড়াও অনেকরকম বড়ো বড়ো গাছ। এই বাগানে কপি, আলু-মুলো, কুমড়ো, চাষ করত হারা ঘোষ, কেষ্ট ঘোষ। হারা বড়ো, কেষ্ট ছোটো— দুই সহোদর। কেষ্ট চাষ কমই করত। তার মূল পেশা চুরি করা— ছিঁচকে চোর যাকে বলে। কলার কাঁদি, মোচা, পাঁঠা-ছাগল, মুরগি-মোরগ, ডাব-নারকেল, যখন যেমন হয়। কেষ্ট বা কেষ্টা নামের ‘নিশিকুটুম্বটি’ সিঁদও দিত মাটির ঘরের দেওয়ালে। সিঁদ কাঠি দিয়ে। হারা ঘোষ অতি রোগে, খুব কালো, প্রায় হাঁটুর কাছে তোলা ধুতি, খালি গা, বাইরে এলে ছিটের ফুল শার্ট হাতা গুটানো। কেষ্ট ঘোষ রঙিন লুঙ্গি-গেঞ্জি, খালি পা, দু-চোখ টকটকে লাল। হারা ঘোষ পায়ে চটি দিত। তো সেই ন্যাড়াপোড়ায় খটখটি বাগান থেকে দড়ি দড়ি হয়ে যাওয়া একদম শুকনো কলাপাতা কাতা দড়িতে বেঁধে পিচ বাঁধানো রাস্তা দিয়ে টেনে আনতে আনতে প্রচুর ধুলো আর ধুলো— ফাগুন-চৈত্রের ধুলো। সেই শুকিয়ে যাওয়া কলাপাতার সঙ্গে শুকনো বাঁশ পাতা, চটের বস্তা বোঝাই করে ন্যাড়াপোড়ার জন্য। খটখটি বাগান থেকে বেগুন চুরি করে আনা হত, কখনও শেষ শীতের ফুলকপি। বেগুন, ফুলকপি গেঁড়িয়ে আনার সময় হারা ঘোষের চোখে পড়লে অবধারিত ভাবে চকচকে ধারাল কাস্তে ছুটে আসত তার হাত থেকে। সেই সঙ্গে অতি অতি কুকথা, কুবাক্য। তো সে যাই হোক। দশ-বারো ফিটের ন্যাড়া হত বহু জায়গায়। আসলে বাঁশের উচ্চতার ওপর নির্ভর করত সব। দীর্ঘ ন্যাড়ার পাশে— দুপাশে ছোটো ছোটো ন্যাড়া। যেন উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটে সোমেন মিত্রর কালী পুজোয় অথবা কলেজস্ট্রিটে ‘ফাটা কেষ্ট’-র কালী আরাধনায় কালীর পাশে ডাকিনি-যোগিনী। ন্যাড়া বাঁধা বেশ ফৈজতের কম্মো। সবাই পারেন না। কায়দা করে, ভালোভাবে বাঁশপাতা জড়িয়ে তাকে গড়ে তোলা হয়। সন্ধেয় আগুন পড়ে ন্যাড়ার গায়ে। বড়ো ন্যাড়ার অগ্নিস্নান সবার শেষে, ছোটো দুটো আগে। ন্যাড়ার মাথাটি পোড়ামাটির ‘পাতিল’— এটি পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বললাম, তার নাক-মুখ-চোখ চুন ও কালিতে অঙ্কিত— ভুতুড়েভাব। ন্যাড়ার পায়ের কাছে ‘ঝাড়াই’ বা ‘ঝাড়িয়া’ করে আনা টাটকা বেগুন, কাঁচকলা। বাড়ি থেকে আনানো গোল আলু, রাঙা আলু, সকরকন্দ— সাদা এবং লাল, যেমন পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে টোম্যাটো— বিলিতি বেগুন, সব পুড়বে ন্যাড়ার আগুনে। গোল আলু, রাঙা আলু, কাঁচকলা, সকরকন্দ— মিষ্টি আলু— লাল এবং সাদা, টোম্যাটো, বেগুন। সেগুলো পুড়ে পুড়ে সেদ্ধ হয়ে গেল, তখন ন্যাড়ার নিভু আগুন থেকে তাদের আধ পোড়া কঞ্চি দিয়ে টেনে বার করে এনে নুন-সহ, অথবা আলুনিই স, মা দেখে বলতেন, এদের মুখ না হনুমান বাঁদরের মুখ, যা পায় তাই যায়। তাই গেলে। ন্যাড়া পোড়ার ‘ন্যাড়া’-র পেটের ভেতর শুকিয়ে যাওয়া কলাপাতার সঙ্গে শুকনো খড়ও দেওয়া হত। দোলের আগে আগে গরুর গাড়ি বোঝাই খড়ের আঁটি গেলেই, তা থেকে টান মেরে দু-চার আঁটি অবলীলায় টেনে নামিয়ে নেওয়া। আর নামাতে নামাতে গো শকটের গাড়োয়ানের বাছা বাছা খিস্তি হজম করা, এতো নৈমিত্তির ব্যাপার ছিল তখন। সেইসব গালাগালকে গায়েই মাখতাম না আমরা। খড়ের আঁটি নিয়ে জমা করা হত, ন্যাড়া পোড়ার জন্য। এভাবেই ন্যাড়াপোড়ার দিনরাত্রি চলে যায় আমাদের সামনে দিয়ে।
Powered by Froala Editor