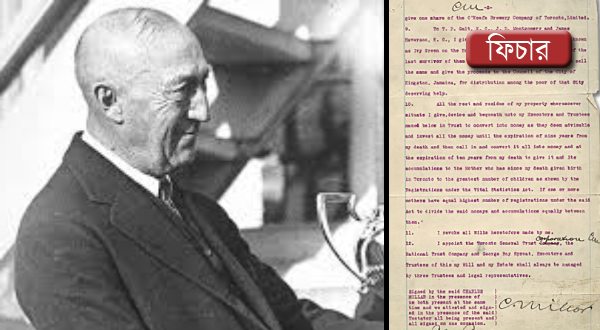সেকালের কলকাতায় শাক্তের বাড়ির পুজোয় সিংহের আকৃতি হত সিংহের মতোই, কিন্তু বৈষ্ণব গোঁসাইদের বাড়ির দুর্গোৎসবে দেখা যেত অশ্বমুখ সিংহ। প্রতিমার আয়তনের ক্ষেত্রেও বংশ অনুযায়ী রকমফের। বড়বাজারের এক বাড়ির প্রতিমা সবচেয়ে ছোটো হত, লোকমুখে তাঁর ডাকনাম ছিল ‘পুতুল দুর্গা’! তখনও ডাকের সাজের প্রচলন হয়নি, প্রতিমাকে মাটির গহনাই পরানো হত। তার সৌন্দর্য ছিল চোখ জুড়নো!
'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' এক আশ্চর্য বই। বিবেকানন্দ-অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর শৈশবের দুর্গোৎসবের স্মৃতিচারণ করেছেন সে-বইয়ের অনেকটা অংশ জুড়ে। অবশ্য, ভেবে দেখতে গেলে, সিংহের আকৃতি সম্পর্কে দত্তমশায়ের এই সাম্প্রদায়িক বিভাজন কি আদৌ সর্বজনীন? তা কিন্তু মনে হয় না। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভবনের স্থায়ী জগদ্ধাত্রী প্রতিমায় বাহনটি নেহাত অশ্বাকৃতিই নয়, সে একটি ঘোড়াই, সিংহসুলভ নখদন্তের বাহার তার একেবারেই নেই। অথচ কৃষ্ণচন্দ্র তো গোঁড়া শাক্ত! ওদিকে বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠিত যে 'মৃন্ময়ী' দুর্গাপ্রতিমা, তাতে কিন্তু সিংহ সিংহের মতোই বহাল আছেন! তাই, আমাদের মতে, সিংহের আকৃতির ক্ষেত্রে ওই ধর্মাচারগত বিভাজনটিকে ঠিক সর্বতোমান্য বলা চলে না।
আর হ্যাঁ, ডাকের সাজের ব্যাপার। ‘ডাকের সাজ’ নামকরণের মূলে আছে ওই গহনার উপকরণের নাম নয়, বরং সেই উপকরণ পরিবহনের মাধ্যমটির নাম। তাই, যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন ততটা উন্নত নয়, তখন সহজলভ্য মাটি দিয়েই বানানো হত ঠাকুরের গহনা, যা প্রতিমার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জুড়ে দিতে হত, আলাদা করা যেত না। পরে, প্রযুক্তি ও পরিবহনের উন্নতির ফলে প্রতিমার সাজসজ্জায় নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যত এসেছে প্রচুর, কিন্তু মাটির গয়না এখনও রয়ে গেছে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের ক্লাসিক নমুনা হিসাবে।
যাই হোক, মহেন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, দুর্গাপুজোয় তখন বেশ ভক্তির ভাব দেখা যেত। ষষ্ঠীর রাত্রে হত বিল্ববরণ। সপ্তমীর সকালে নবপত্রিকার স্নান থেকে শুরু করে, শহরে আনন্দের স্রোত বইতে শুরু করত। সন্ধিপুজোয় দীপমালার আয়োজন হতো। তখন অনেক ভদ্রমহিলা নিজেদের মানসিক ব্রত পূর্ণ করার জন্য ঠাকুরের সামনে হাতে বা মাথায় সরা নিয়ে ধুনো পোড়াতেন। অনেকে সন্ধিপুজোর সময় নাপিতের সাহায্যে বুক চিরে রক্ত বের করে, সোনার বা রূপোর বাটিতে করে পুজো দিত। তবে এই প্রথা খুব বেশি দেখা যেত না। কলকাতা শহরে অনেক বাড়িতেই তখন বলি হত না। শাক্ত হলেও, কোনো কোনো পরিবারে বংশ পরম্পরায় বলি নিষেধ ছিল।
বলির সংখ্যা কম হলেও বলি নিয়ে সেকালের ছেলেপুলেদের আগ্রহ যে কিছু কম ছিল না, তারও প্রমাণ মিলবে রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' বইতে। তাঁর খেলনা সিংহকে তিনি যে কতবার খেলাচ্ছলে বলি দিয়েছেন! আবার এজন্য একটি স্বরচিত মন্ত্রও বানিয়েছিলেন তিনি -
"সিঙ্গিমামা কাটুম
আরও পড়ুন
দুর্গার জন্য গান স্যালুট; কলকাতার ‘বন্দুকওয়ালা বাড়ি’তে অভিনব অভ্যর্থনা দেবীর
আন্দি বোসের বাটুম
উলুকুট ঢুলুকুট ঢ্যাম কুড়কুড়
আখরোট বাখরোট খট খট খটাস
আরও পড়ুন
রোজ সাইকেলে কলকাতা, মাত্র ৫ টাকায় মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন রানাঘাটের যুবক
পট পট পটাস।"
সে সময় বাচ্চা ছেলেদের একটা বড়ো আমোদের ব্যাপার ছিল নীল মাখানো কোরা কাপড় পরে ঢুলিদের বাজনার তালে তালে নাচা। তখন ছোটদের জন্য নীল রং মাখান কোরা তাঁতের কাপড়ই বরাদ্দ ছিল। ধোয়া কাপড় বয়োজ্যেষ্ঠরা পরতেন। সেই কাপড় পরেই ছেলেদের আনন্দ দেখে কে? "কাঁইনানা, কাঁইনানা, গিজদা গিজোর, গিজোড় গিজোড়" তালে তালে নেচে উঠত তারা। ঢুলিদের আরেকটা বোলও দারুণ জনপ্রিয় ছিল- "দাদাগো দিদিগো গাবতলাতে গরু দেখ্সে; গরু গরু গরু গরু তার দেখব কি আর।"
ছোটোদের আর বড়োদের এই সম্পূর্ণ পৃথক মহলের ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেও সত্য বলে যাচিয়ে নেওয়া যায়। তিনিও লিখেছেন, তাঁর ছেলেবেলায় ঠাকুরবাড়ির মতো ধনীগৃহেও শিশুদের জামাকাপড় সম্পর্কে অতিরিক্ত সাদামাটা করে তোলার একটা প্রবণতা ছিল। শীতে একটা সাদা জামার উপরে আরেকটা সাদা জামাই ছিল যথেষ্ট, বয়স দশের কোঠা পার হবার আগে কোনোভাবেই মোজা পরার সৌভাগ্য হত না, এমনকি জামায় পকেট-যোজনাও করা হত না। মনে হয়, শৈশব থেকে সন্তানদের সংযত জীবনে অভ্যস্ত করে তোলার একটি সামূহিক মনোবৃত্তিই এর কারণ ছিল।
আরও পড়ুন
কমছে চাহিদা, বিলুপ্তির পথে বাংলার প্রথম ‘ব্র্যান্ডেড মিষ্টি’
তখনকার দিনে বাড়িতে দুর্গাপুজো হলে দশজনকে পাত পেড়ে খাওয়ানোর রীতি ছিল। ব্রাহ্মণের বাড়ি হলে ভোজ্য তালিকায় থাকত ভাত, পাঁচরকম তরকারি, দই আর পরমান্ন। শাক্ত ব্রাহ্মণ হলে পাতে মাছ পড়ত। কায়স্থ বাড়িতে লুচির ফলার হত। সাদামাটা হলেও, সকলকে খাওয়ানো চাইই চাই! তবে বামুন বাড়ির শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট ইত্যাদি রান্না হতো অতি উপাদেয়, বাড়ির মেয়েরা নিজেরাই এসব রাঁধাবাড়া করতেন। সন্ধ্যার সময়ে ঝি, চাকর, ছেলেমেয়েদের বেড়াতে নিয়ে গেলে এক সরা করে জলপান দেবার প্রথা ছিল। আর মিষ্টিমুখ তো লেগেই থাকত!
ভোজের এই বিবরণ থেকে দুটি জিনিস স্পষ্ট হচ্ছে। এক, তখনও যজ্ঞিবাড়িতে রসুয়ে বামুনদের ক্যাটারিং সিস্টেমের চল হয়নি, রান্নার দায়িত্ব পরিবারের ভদ্রমহিলাদের হাতেই আছে। আর দুই, শাস্ত্রবিধি ও লোকাচারের প্রাবল্যে গৃহকর্তা তথা আয়োজকের জন্মগত জাতি অনুযায়ী ঠিক হচ্ছে খাদ্যতালিকায় অন্নের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি। এই নিয়মকে সমাজের সকলেই তখন মুখ বুজে মেনে চলছেন, বিদ্রোহ করছেন না। বিদ্রোহ এসেছে পরে, জানবাজারের রাণী রাসমণির দাপটে, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-অগ্রজ রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিধান অনুসারে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে মা ভবতারিণীকে অন্নভোগ দেওয়ার প্রচলন করেছিলেন। এরপর আস্তে আস্তে এই খাদ্যাখাদ্য বিচারের গোঁড়ামিতে ধরেছে ভাঙন, আর এখনকার বাঙালি সমাজে তো তা এক প্রকার অদৃশ্য বলা চলে।
দত্তমশায় লিখছেন, বিজয়ার দিন পাড়ার বুড়ো ব্রাহ্মণদের প্রণাম করার সময় কিঞ্চিৎ প্রণামী দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। তখন বিজয়ার কোলাকুলিতে সন্দেশ বা অন্য কোনো খাবার চলত না। বিজয়াদশমীর স্পেশাল মিষ্টান্ন ছিল নারিকেলছাবা!
তখনকার দিনের পুজোয় অনেক ভট্টচার্য বামুন বার্ষিকী পেতেন। পরে এই প্রথা উঠে যায়। বিজয়ার রাত্রে সকলেই পরস্পরের বিরোধ ভুলে কোলাকুলি করত। তখন মাসে মাসে দোকানের টাকা শোধ করার রীতি ছিল না। কথায় ছিল ঢাকে-ঢোলে, অর্থাৎ দুর্গাপুজো আর চড়কে লোকে দেনা চুকিয়ে দিত। তখন মুদির দোকান থেকে উটনো নেওয়ার প্রথা ছিল - বছরে দুবার তা পরিশোধ হত।
সকলের কাছেই দুর্গাপূজা ছিল মহা আনন্দের উৎসব। গ্রাম্য মুসলমানরাও তখন ঠাকুর দেখতে এসে প্রতিমাকে তিনবার সেলাম সেলাম সেলাম বলে সম্মান দেখাতেন। যাদের বাড়িতে প্রতিমা এনে পুজো করা সম্ভব হত না, তারা কয়েকদিন চণ্ডীপাঠের আয়োজন করতেন।
দুর্গাপুজো হিন্দুমাত্রেরই অবশ্যকর্তব্য, স্মার্ত শাস্ত্রের বিধান এমনই। দেখা যাচ্ছে, তখন পুজোর অনুকল্প হিসাবে বাড়িতে বাড়িতে স্বধর্মনিষ্ঠ মানুষেরা সেই কদিন চণ্ডীপাঠের আয়োজন করতেন। পরে, আস্তে আস্তে এই অনুকল্পে আরও শর্টকার্ট দেখা দিয়েছে, চণ্ডীপাঠের স্থান নিয়েছে মহাষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি। এবং, এই মহাষ্টমীর দিনই এখন ছেলেদের পাঞ্জাবি আর মেয়েদের শাড়ি পরার দিন, অর্থাৎ অতীত-ঐতিহ্যকে ফিরে দেখার দিন, আরও একবার যাপনের দিন।
এই ছিল তখন কলকাতার জাতীয় উৎসব। ভক্তিভাব ও জাতীয়ভাবের সংমিশ্রণে, সে এক মহা আনন্দের পার্বণ! রীতি-রেওয়াজ হয়তো বদলেছে, কিন্তু আজও মানুষ কলকাতার সেরা উৎসব বলতে, দুর্গাপুজোই বোঝে!
Powered by Froala Editor