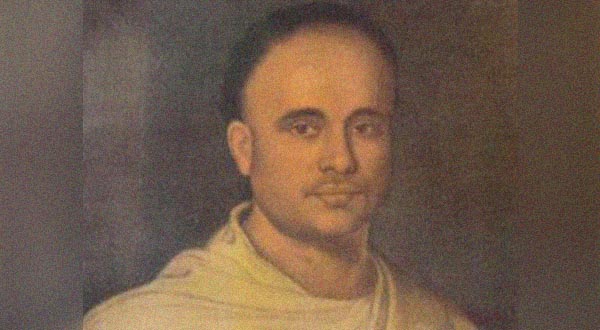তত্ত্বে বাঁধা পড়া নয়, কাজ হোক হাতে-কলমে। সকৃতজ্ঞ স্মরণে আজ যাঁর সামনে নতজানু বর্তমান, অতীতে ফিরে দেখি, সেই মানুষটার মূলমন্ত্র যেন ছিল এটাই। কাকতালীয়ই হবে, তবু যে ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের প্রয়াণ, সে-বছরই জন্ম নিচ্ছেন আনতেনিও গ্রামশি। যিনি বহু পরে ‘অরদিনে নুওভো’ পত্রিকায় খোলসা করে জানাবেন, স্রেফ বাগ্মিতা নয়, নব্য বুদ্ধিজীবীকে সরাসরি নির্মাতা, সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। অর্থাৎ, স্রেফ গাণিতিক স্তরে নয়, যাঁর বিচরণ হবে ফলিতে। এবং তাঁর সে যাত্রার অভিমুখ হতে হবে ইতিহাসের মানবিকবাদী ধারণায়। নতুবা কেউ একজন বিশেষজ্ঞ কিংবা বিশেষজ্ঞ রাজনৈতিক থেকে যাবেন মাত্র, অগ্রগণ্য ভূমিকায় পৌঁছাতে পারবেন না।
বহুবার ইতর ব্যবহারে হতকুচ্ছিত হয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবী শব্দটিকে আমরা সরিয়েই রাখলাম, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বহুদিন আগেই যে এই সমস্ত স্তর অতিক্রম করে একেবারে অগ্রগণ্যের ভূমিকাতেই পৌঁছেছিলেন তা স্পষ্ট। সেই মত, সেই জেদ ও সংস্কারের মুক্তমন তৈরি হয়েছিল এই বাংলাতেই। সেই প্রথম আলোর উদয় তাঁর অন্তরেই। সত্যিই তিনি বিধাতার আশ্চর্য ব্যতিক্রম।
শোনা যায়, নদিয়া-শান্তিপুরী তাঁতিরা বিদ্যাসাগর পেড়ে শাড়ি তৈরি করতেন। আর তাতে লেখা থাকত বিধবাবিবাহ সমর্থনের গান। আবার হাটে হাটে, গ্রামের পথে যেতে যেতে গাড়োয়ানরা, এমনকি কৃষকরাও তাঁর হয়ে গান গাইতেন। অবশ্য বিপক্ষের গান কিছু কম ছিল না। কিন্তু এ-উদাহারণ টানার কারণ এই যে, একজন মানুষ যে বহুজনের সম্মতি আদায় করতে পারেন, তার মূল ওই হাতেকলমে কাজে।
বিধবাবিবাহ, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মতে যা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ, তা দিয়েই শুরু করা যাক।
বিধবাবিবাহ প্রচলন নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল বহুদিন আগে থেকেই। বলা যায়, পরিসরটা তৈরি হয়েছিল ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন এবং রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কারের পথ ধরে। এরই মধ্যে বিধবাবিবাহ কেন হওয়া উচিত তা-নিয়ে পরপর দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন বিদ্যাসাগর। তাত্ত্বিক বিতণ্ডা তাতে চরমে ওঠে। গোঁড়ারা যেমন প্রতিবাদ করেন, বিদ্যাসাগরও পরাশর সংহিতা থেকে প্রমাণ তুলে দেখান যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরোধী নয়। কিন্তু এ তো গেল বৌদ্ধিক চর্চার বিষয়। এরপরই বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের পক্ষে একটি স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র তৎকালীন সরকারের কাছে জমা দেন। মনে রাখতে হবে, তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন মোটে ৯৮৭ জন। বিরুদ্ধপক্ষই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এই যে নিজের যুক্তি-তত্ত্ব-তথ্য হাতিয়ার করে বিদ্যাসাগর ‘গণতান্ত্রিক’ পথেই এগিয়েছিলেন, তার ফল মিলেছিল অচিরেই। ১৮৫৫-এর অক্টোবরে এই আবেদনপত্র জমা পড়ে। ১৮৫৬-এর জুলাইয়ে বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হয়। স্পষ্টতই, প্রতীয়মান, একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কীভাবে ফলপ্রসূ করে তুলতে হয়, এমনকি মুষ্টিমেয়র সমর্থন থাকলেও যে লড়াইয়ে নামলে জয় ছিনিয়ে নেওয়া যায়, তা সেদিন প্রমাণ করে দিয়েছিলেন তিনি। আজও যখন আমাদের প্রতিবাদ ভার্চুয়াল পৃথিবীর চৌকাঠে মাথা ঠোকে, তখন তাঁর পদক্ষেপ দৃষ্টান্ত। মূলমন্ত্র অবশ্যই কথায় দড়ো না হয়ে, কাজে করে দেখানো। এ-ব্যাপারে ব্যর্থতা যে একদম নেই, তা নয়। বহুবিবাহ রোধে আইন প্রণয়ন অবশ্য করাতে পারেননি। কিন্তু আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তার প্রভাবও হয়েছিল জোর। উত্তরকাল তার সাক্ষী থেকেছে।
বস্তুত এই কাজে করে দেখাতে গিয়েই চাকরি জীবনের একেবারে গোড়াতেই হেনস্তা হতে হয়েছিল তাঁকে। ১৮৪৬ সাল। সংস্কৃত কলেজে চাকরি নিয়েছেন। দেখলেন, কলেজে শিক্ষার হাল বেশ খারাপ। না শিক্ষকদের আসা-যাওয়ার সময় আছে। না আছে পাঠ্যের ঠিক-ঠিকানা। এখান থেকেই শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগরের আত্মপ্রকাশ। সবকিছু একেবারে ঢেলে সংস্কারের পরিকল্পনা নিলেন তিনি। আর গোল বাধল প্রধান সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে। অবধারিত মতবিরোধ। এবং বিদ্যাসাগরের চাকরিত্যাগ। সম্পাদকের প্রশ্ন ছিল, চাকরি গেলে বিদ্যাসাগরের চলবে কী করে? বিদ্যাসাগরের জবাব ছিল, আলু-পটল বেচে খাব।
তা কষ্ট স্বীকার কম করতে হয়নি। কিন্তু শিক্ষার সংস্কারের যে-কাজে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন তা ছাড়েননি কখনও। শিক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কার ও ভাষা-সাহিত্যের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অগ্রগণ্যেরই।
প্রথমত, শিক্ষা না-থাকলে যে সমাজ বদলাবে না, তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। এই উদ্দেশ্যেই শিশুশিক্ষার জন্য ‘বর্ণপরিচয়’ রচনা। আবার, এক বন্ধুকে সংস্কৃত শেখাতে গিয়ে বুঝেছিলেন, এই শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিতেও বদল আনতে হবে। সেই হেতু সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনার প্রয়াস। এ ছাড়া অন্যান্য অনুবাদ তো ছিলই।
দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষার ছত্রখান রূপকে তিনিই প্রথম কমার শাসনে বাঁধলেন ও দিলেন এক আঁটোসাটো গোছানো চেহারা।
তৃতীয়ত, শুধু লেখক হিসেবেই ক্ষান্ত থাকেননি, নিজেকে তিনি বলতেন ‘লেখক-ব্যবসায়ী’। মদনমোহন তর্কালংকারের সঙ্গে একযোগে সংস্কৃত প্রেস নামে প্রকাশনা শুরু করেন।
এ যেমন একটা দিক। অন্যদিকে শিক্ষা-সংস্কারক হিসেবে, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ- স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার। তা নিয়েও বেজায় বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু একগুঁয়ে মানুষ, যা করবেন ভেবেছিলেন করেই ছেড়েছেন। বালিকা বিদ্যালয় গড়ার জন্য দৌড়েছিলেন ছোটোলাট অবধি। এবং সম্মতি আদায়ও করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে মেদিনীপুর, হুগলি, নদিয়া, বর্ধমান জেলায় তিরিশটিরও বেশি বালিকা বিদ্যালয় শুরু হয়েছিল।
অর্থাৎ, এযাবৎ বিদ্যাসাগরের মহাশয়ের কর্মকাণ্ডের দিকে ফিরে তাকালে আমরা স্পষ্টত দুটি দিক দেখব, একদিকে সমাজের জঙ্গমতা ভাঙতে বিশেষত নারীমুক্তিতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন। অন্যদিকে, শিক্ষা-ভাষা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে অনলস তিনি। তার জন্য যা যা করার দরকার করছেন নির্দ্বিধায় ও সমস্ত ত্যাগ সহ্য করেই।
এরপরেও বাকি থেকে যায় আর-একটি অন্যতম দিক। তা হল এক তীব্র আত্মসম্মানবোধে জারিত বাঙালিয়ানা লালন করে চলা। অর্থে বা বিত্তে বড় হলেই যে সংস্কারের অগ্রণী হওয়া যায়, এহেন ধারণা আজও অনেকে পোষণ করেন। এখানেও সার্থক ব্যতিক্রম বিদ্যাসাগর। চাকরি না-থাকা অবস্থায় বাংলার ইতিহাস লিখেছিলেন তিনি। আজীবন বাঙালিদের বৃহত্তর অংশের থেকে কটূ-কাটব্যই শুনে এসেছেন। কিন্তু একদা এক পরিচিতজনের কাছে থাকা মোহরে বাংলা ভাষা দেখে তা যে রাজভাষা ছিল, তার প্রমাণে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে আসলে তিনি লড়াইটা শুরু করেছিলেন অনেকটা গভীর থেকে। প্রথমে শিক্ষার আলো, সেই সঙ্গে আপন জীবনে অনুশিলীত চারিত্রিক দৃঢ়তা আর আত্মসম্মানবোধের দৃষ্টান্ত – বস্তুত এই সবই-ই জন্ম দিতে পারে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সমস্ত রকম সংস্কারমুক্তির স্বাধীনতা। যে-স্বাধীনতা আজও হয়তো দেশ অর্জন করতে পারেনি। সেই সর্বার্থে মুক্ত দেশের স্বপ্ন দেখা প্রথম মানুষ নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগরই। রামকৃষ্ণ আর বিদ্যাসাগরের ভাবনার ধারা এক স্রোতে মেলেনি। তবু মনে মুখে এক হওয়ার যে স্বাধীনতা ও সেই হেতু কৃচ্ছ্রসাধন – সেই বিন্দুতে দুজনেই হয়তো মিলেছেন। আজ সমস্ত স্বাধীনতার লড়াই তাই তাঁকে প্রণাম জানায়। কেন-না তিনি জীবন দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন এক মহতী শিক্ষা, যা কর্তব্য তা পালন করতে হবে। এর অন্যথা নেই। এ ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো পন্থাও নেই। আজও।